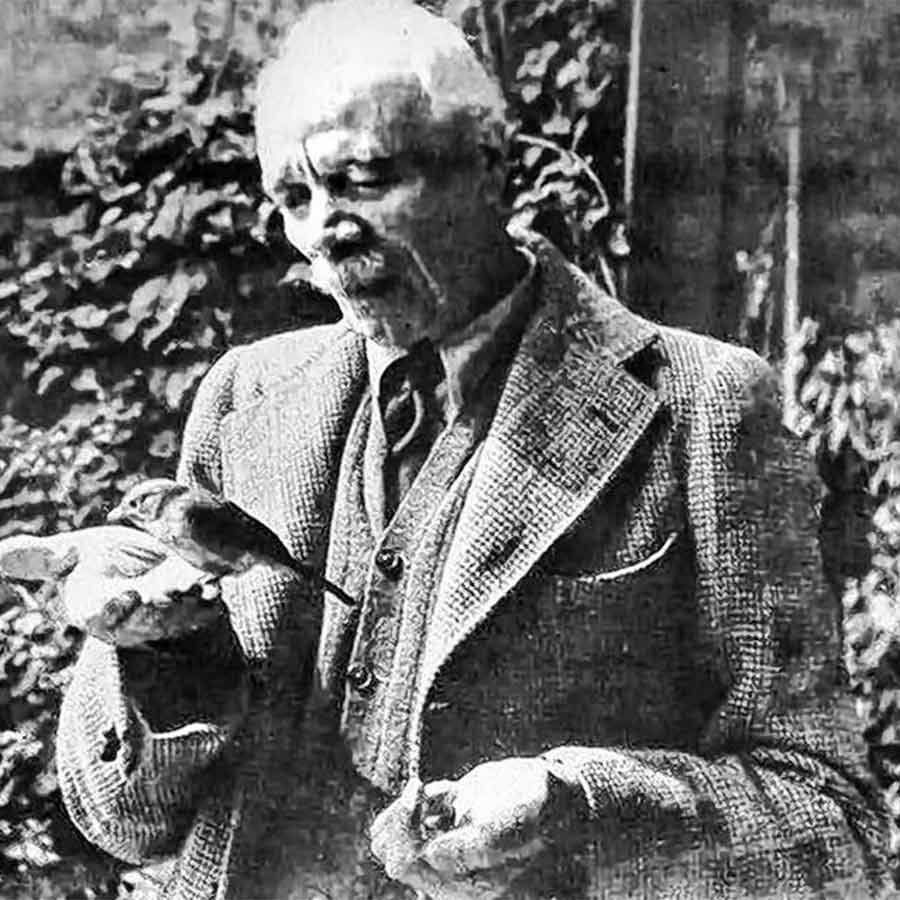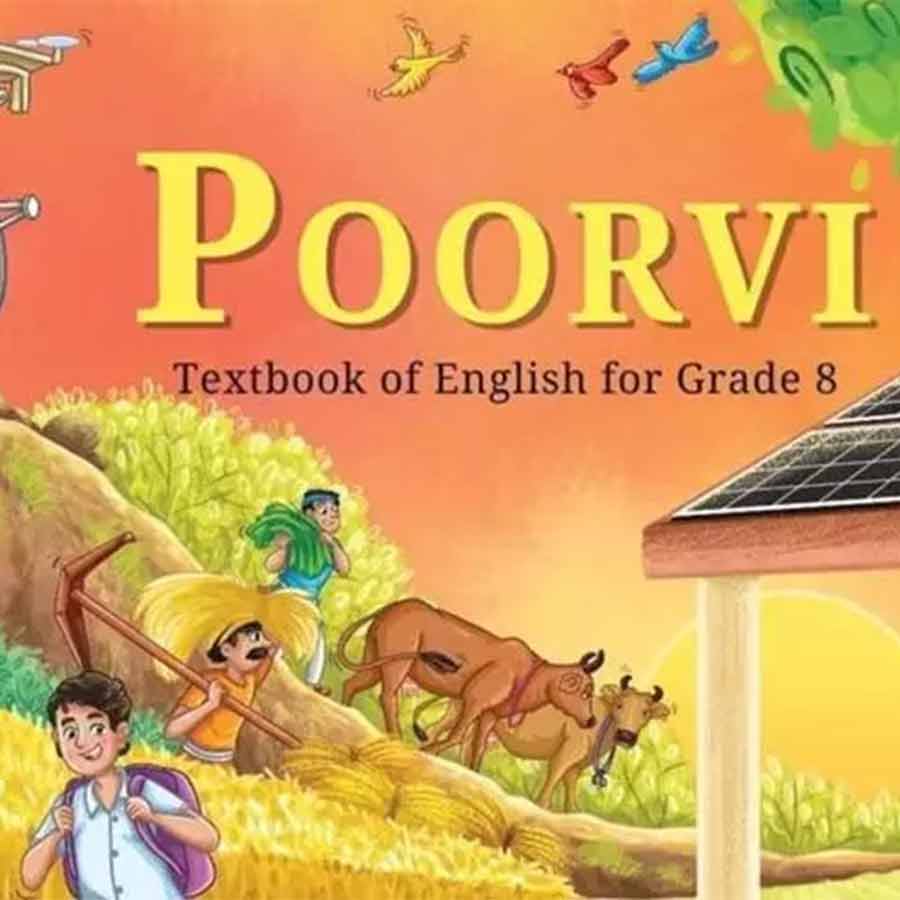অর্থমন্ত্রীর বাজেট-ভাষণে ঐতিহাসিক কর-ছাড়ের কথাটি প্রকাশিত হওয়ায় তার কয়েক সপ্তাহের মাথায় সংসদে নতুন আয়কর আইন পেশ হওয়া নিয়ে তেমন হইচই হল না। কর-ছাড়ই অবশ্য এই নতুন বিলের একমাত্র দিক নয়। এতে আয়কর আইনের জটিলতা কমানোর যে চেষ্টা হয়েছে, তাকে স্বাগত জানানোই বিধেয়। যেমন, এত দিন অবধি আয়করের ক্ষেত্রে ফাইনানশিয়াল ইয়ার, প্রিভিয়াস ইয়ার, অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার ইত্যাদি ধারণা ছিল, যা সাধারণ করদাতাদের কাছে বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত। এই শব্দবন্ধগুলিকে বাতিল করে নতুন বিলে চালু হল ট্যাক্স ইয়ার কথাটি। অতঃপর একটি আর্থিক বছরের মধ্যেই করের হিসাব সীমাবদ্ধ থাকবে। আইনের ভাষাও আগের চেয়ে সহজ করা হয়েছে। ‘নটউইদস্ট্যান্ডিং’-এর মতো শব্দকে বিদায় দেওয়া হয়েছে; যে সব শব্দ বহুবিধ মামলার কারণ হয়ে দাঁড়াত, সেগুলির মধ্যেও অনেকগুলিই নতুন বিলের গা থেকে ঝরে গিয়েছে। ১৯৬১ সালের আয়কর আইন থেকে বাদ পড়েছে বেশ কিছু অচল ব্যবস্থা, অতীতগন্ধী নিয়ম। আবার, পুরনো আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারায় ছড়ানো ছিল কর-ছাড়ের বিভিন্ন নিয়ম। করদাতাকে খুঁজে বার করতে হত সেগুলি, অথবা সাহায্য নিতে হত পেশাদারদের। নতুন আইনে যে করগুলি প্রযোজ্য হবে, সেগুলিকে একত্র করে একটি ধারার অন্তর্গত করা হয়েছে। এমন নয় যে, আগের ব্যবস্থায় আয়করদাতার পক্ষে ছাড়ের ধারাগুলি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু, ব্যবহারকারীর সুবিধার কথা ভাবা আধুনিক আইনব্যবস্থার একটি দায়ও বটে। এই বিলটি সেই দায় নির্বাহ করেছে।
এমন নয় যে, নতুন আয়কর বিলে কোনও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধিত হয়েছে, ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে দেওয়া হয়েছে। তার প্রয়োজনও ছিল না। এই বিলের মূল লক্ষ্য ছিল আইনকে সহজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, অচল ব্যবস্থাগুলি বিলোপ করা। লক্ষ্যটি বর্তমান শাসকদের আইন সংস্কারের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে মূল কথা হল, আইনের গা থেকে ইতিহাসের চাপিয়ে দেওয়া বাহুল্য ও জটিলতা ছেঁটে ফেলা, অবান্তর ধারা বিলোপ করে তাকে তুলনায় সহজ করে তোলা। ভাষার জটিলতা এবং অস্পষ্টতা আইনকে চরিত্রে দীর্ঘসূত্রী করে তোলে, বিবিধ মামলার অবকাশ তৈরি হয়। সে দিক থেকে এই সংস্কারের প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানানোই বিধেয়। অন্তত ভারতের মতো দেশে, যেখানে সমগ্র বিচারব্যবস্থা বিবিধ কারণে অতি শ্লথ গতিতে চলে।
তবে, বহুতর প্রশ্নেরও অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, গত কয়েক বছর ভারতে দ্বৈত করব্যবস্থা চালু ছিল, চলতি ভাষায় যার নাম ‘ওল্ড ট্যাক্স রেজিম’ এবং ‘নিউ ট্যাক্স রেজিম’। এই বাজেটে যে কর-ছাড় ঘোষিত হয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র নিউ ট্যাক্স রেজিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাতে যে হিসাব দাঁড়াচ্ছে, সম্ভবত কোনও করদাতার কাছেই আর পুরনো ব্যবস্থাটি অধিকতর লাভজনক হবে না, ফলে সেটি কার্যত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও উল্লেখ এই কর বিলে নেই। দ্বিতীয়ত, এত দিন অবধি কৃষি আয় করযোগ্য ছিল না— নতুন বিলে কিছু ক্ষেত্রে কৃষি আয়ের উপরে কর বসানোর অবকাশ রয়েছে। কিন্তু, অন্যান্য ক্ষেত্রে আইনটি যেমন স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে, কৃষি তার ব্যতিক্রম। সেখানে হরেক শর্ত, হরেকতর ছাড়। প্রয়োজন ছিল না। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে যেমন বারো লক্ষ টাকা অবধি আয় করহীন হতে চলেছে, কৃষির ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হলেই যথেষ্ট হত। তৃতীয়ত, আয়করে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তাতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হবে এক লক্ষ কোটি টাকা, বা দেশের মোট রাজস্বের প্রায় তিন শতাংশ। জনসংখ্যার মাত্র তিন-চার শতাংশের জন্য এই বিপুল ছাড় শেষ অবধি ন্যায্যতার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হবে, না কি তা বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সুবিধাবাদ হিসাবে পরিগণিত হবে, সে প্রশ্নটিও থাকছে।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)