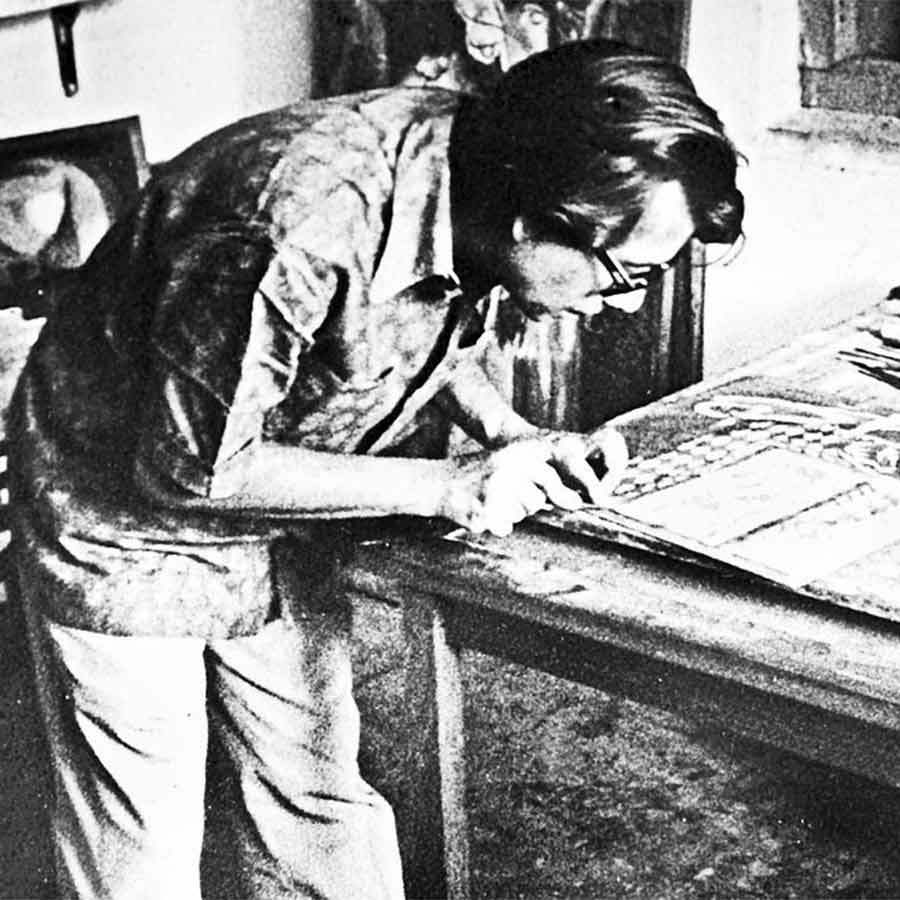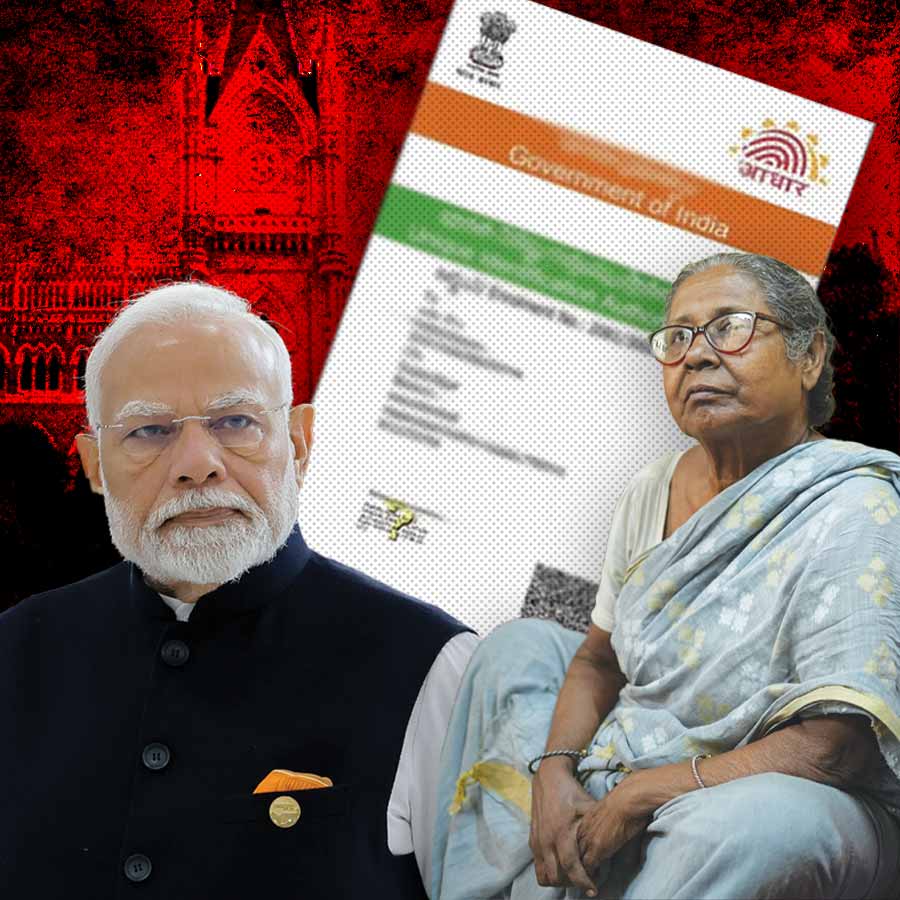শিল্পকলার জগৎ বলতে আজও আমরা প্রধানত চিত্র আর ভাস্কর্যের দিকে নির্দেশ করে থাকি। পৃথিবীর বিখ্যাত সব আর্ট গ্যালারির অন্দরে স্বমহিমায় বিরাজ করছে অগণিত ছবি আর ভাস্কর্য। তুলনায় ছাপাই ছবির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে কিছু কাল পরে। ভেবে দেখলে, এই আধুনিক শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে কারিগরি দক্ষতার এলাকা বিশেষ ভাবে সংগ্রথিত। সে কাঠখোদাই হোক বা লিথোগ্রাফ অথবা এচিং— সবের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে আঙ্গিকের খুঁটিনাটি, টেকনিকের পারিপাট্য। ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে লিথো-স্টোন বা ধাতব পাতের উপরে ছবিটি রচিত হলেই শিল্পীর কাজ শেষ হয়ে যায় না। চূড়ান্ত প্রিন্ট নেওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত শিল্পীকে সতর্ক থাকতে হয়। সেই সঙ্গে স্মরণীয়, ছাপাই ছবির নিখুঁত প্রিন্ট নেওয়াও শিল্পীর কাজের এক জরুরি অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে অন্যতম ‘প্রায়োরিটি’ বলে গণ্য করা হয়।
আমাদের দেশে ছাপাই ছবির দিকপাল শিল্পীদের মধ্যে সোমনাথ হোর, কৃষ্ণা রেড্ডি প্রমুখ সকলেই এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলেন। পাশাপাশি এখানে অনায়াসে উচ্চারিত হবে সনৎ করের নাম। এক দিকে তিনি যেমন ছাপাই ছবির আঙ্গিকের নিরীক্ষায় আজীবন নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, অন্য দিকে প্রগাঢ় অনুসন্ধানী মন নিয়ে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ছাপাই ছবির অন্দরমহল। এই অনুসন্ধিৎসা যেমন তাঁর নিজের জন্য, তেমনই তা মেলে ধরতে চেয়েছেন ছাত্রদের সামনে। ছাত্রেরা যেন অভ্যাসের দাগা বুলিয়ে শিল্পের কাজ চালিয়ে না যায়— এই ছিল শিল্পী ও শিক্ষক সনৎ করের ঐকান্তিক প্রয়াস। হাতেকলমে কাজের পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে তিনি গভীর ভাবে পড়াশোনা করেছেন, খুঁজতে চেয়েছেন বিশ্বের অন্যত্র কী ভাবে বিবর্তিত হয়েছে ছাপাই ছবির ইতিবৃত্ত।
নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়, কেবল কৃতী শিল্পী নন, তিনি ছিলেন ছাত্রের অন্তরে প্রশ্ন উস্কে দেওয়া তন্নিষ্ঠ শিক্ষক। সেই সঙ্গে এক জন দক্ষ সংগঠক, সুপরিচালক। ‘সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস’ নামে বিখ্যাত শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। শিল্পচর্চা ও শিক্ষকতার ফাঁকে তিনি লিখে রেখেছেন শিল্পীজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিজীবনের নানা স্মৃতি। সেই সব লেখা, তাঁকে ঘিরে আলোচনা ও চিঠিপত্র, এবং শিল্পীর একগুচ্ছ ছবি একত্রিত করে গ্রন্থমালার আকারে দেবভাষা প্রকাশ করছে সনৎ কর: জীবন ও শিল্প সিরিজ়, এটি তার দ্বিতীয় খণ্ড। অত্যন্ত মূল্যবান এই গ্রন্থে কেবল সনৎ করের জীবন ও শিল্পের কথাই উঠে আসেনি, প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের শিল্পকলার সমগ্র প্রেক্ষাপট। সে দিক থেকে এ বই আমাদের সাম্প্রতিক শিল্প-ইতিহাসের প্রত্যক্ষ দলিলও বটে।
প্রচ্ছদে মুদ্রিত শিরোনামের সঙ্গে বইয়ের নামপত্রে সংযোজিত হয়েছে আর একটি টুকরো। উপশিরোনাম হিসেবে সেখানে লেখা, ‘শান্তিনিকেতন, প্রথম পর্ব (১৯৭৪–২০০০)’। অর্থাৎ প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর শান্তিনিকেতন পর্বের প্রথমাংশ। শান্তিনিকেতনের পরবর্তী পর্ব ঘিরে আর একটি খণ্ড প্রকাশিত হবে বলে অনুমান করি। গ্রন্থের বিষয়সূচি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। সেগুলি যথাক্রমে ‘শান্তিনিকেতন পর্ব’ (দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়), ‘সনৎ করের রচনা’, ‘প্রসঙ্গ সনৎ কর’ এবং ‘উত্তর প্রত্যুত্তর’। পাশাপাশি রয়েছে সম্পাদকীয় বক্তব্য ‘শুরুর কথা’ এবং রচনার তথ্যসূত্র ও টীকা। মাঝে সাতটি বিভিন্ন অংশে শিল্পীর চিত্রাবলি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে— যেগুলি রচনাকালের ক্রম হিসেবে নির্বাচিত। সব মিলিয়ে বইটি প্রকাশের নেপথ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট। সম্পাদকীয় বক্তব্যে প্রকাশ, “এখানে শিল্পী রচিত শিল্প সংক্রান্ত, নান্দনিক বোধকে কেন্দ্র করে একাধিক রচনা সংকলিত হল। দেশীয় শিল্পকলা থেকে বিশ্ব শিল্পভুবন এই প্রদক্ষিণে উঠে এসেছে।” আরও বলা হয়েছে, “তবে এই অধিকাংশ রচনাসমূহই কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা হিসেবে যে তিনি লিখেছিলেন তা হয়তো নয়, অধ্যাপনার সূত্রে, সেমিনার সূত্রে এইসব লেখা রচিত হয়েছিল যা প্রকৃত অর্থে শিল্পীর নিজস্ব অনুসন্ধান, এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ‘বলার মতো কিছু না’ যা শিল্পীর আত্মজীবনকেই উন্মোচিত করে।” সে দিক থেকে গ্রন্থে মুদ্রিত শিল্পীর অনেকগুলি লেখা এই প্রথম পাঠকের সামনে এল।
‘সনৎ করের রচনা’ অংশে চারটি লেখা— ‘কাঠখোদাইয়ের ইতিবৃত্ত’, ‘জাপানি ছাপচিত্র’, ‘ভারতীয় চারুকলার আধুনিকতা ও তার উদ্ভব’ এবং শিল্পীর আত্মকথার আদলে রচিত ‘বলার মতো কিছু না’ পর পর মুদ্রিত। প্রথম তিনটি লেখায় ছাপাই ছবি শিল্পকলার যে সামগ্রিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান। শুরুর লেখাটি কেবল বাংলা তথা ভারতীয় কাঠখোদাই ছবির পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, উঠে এসেছে চিন-জাপান ও ইউরোপীয় কাঠখোদাইয়ের কথা, এসেছে ফরাসি ও ইটালীয় শিল্পীদের কাজ আর ভারতীয় রিলিফ-প্রিন্টের বিস্তার-সহ বাংলাদেশের কথা। অমুদ্রিত এই রচনা শুধু শিক্ষার্থীদের কাছে নয়, শিল্পরসিকদের কাছেও বিশেষ মূল্যবান। ‘ভারতীয় রিলিফ প্রিন্ট’ অংশে আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, “ভারতবর্ষের প্রথম রিলিফ প্রিন্ট প্রথায় কাঠখোদাই, লিনোকাট ইত্যাদি নিয়ে শুধুমাত্র নান্দনিক ভাব প্রকাশের তাগিদে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় নন্দলাল বসু-র উৎসাহে। বইয়ের সচিত্রকরণের ইতিহাসে নন্দলাল বসুর রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ-এর লিনোকাট সচিত্রকরণগুলি সু-রুচির এক নতুন অধ্যায় শুরু করে। ক্রমে, এই শান্তিনিকেতনেই পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে লিনোকাট মাধ্যমে ছবি করানো শুরু হয়,” যা খুবই জরুরি কথা। সহজপাঠ-এ নন্দলালের ছবিগুলি সচিত্রকরণের মার্কায় ভূষিত করা চলে না, এগুলি শিল্পের অনবদ্য উপমায় উত্তীর্ণ।
‘ভারতীয় চারুকলায় আধুনিকতা ও তার উদ্ভব’ রচনায় ভারতীয় শিল্পের ধারাবাহিকতা নিয়ে জরুরি আলোচনা বিধৃত। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখেছেন, “আধুনিকতার মূল লক্ষ্য ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা। শিল্পী তাঁর নিজের দেখার, বোঝার আর মনের প্রকাশ ঘটাবেন তাঁর শিল্পকর্মে— তার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস-সচেতন হবেন। আর রবীন্দ্রনাথই আমাদের এই পথের দিশারী, যা তিনি পেয়েছিলেন ভারত আত্মার অন্তরে ডুব দিয়ে। তিনিই দেখিয়েছেন তাঁর আন্তর্জাতিকতার মধ্যে দিয়ে যে, আমাদের নিভে যাওয়া প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে হবে পশ্চিমের জাজ্বল্যমান প্রদীপ থেকে। রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথই অনুসৃত হচ্ছে বর্তমান প্রবীণ, তরুণ ও তরুণতর শিল্পীদের দ্বারা, যার শুরু বিশ শতকের গোড়ার দিকে।” এই কথাগুলি নিয্যস সত্য।
তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা, ‘বলার মতো কিছু না’ লেখাটির ধরন এবং স্বাদ চমৎকার। ১৯৯২ সালে দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় এবং পরে স্বতন্ত্র বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে এই লেখা। এখানে পাঠকের উপরি পাওনা লেখার সঙ্গে সনৎ করের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সাজিয়ে দেওয়া অজস্র মূল্যবান ফোটোগ্রাফ। স্বতন্ত্র একটি যুক্ত হয়েছে শিল্পীর প্রথম প্রদর্শনী প্রসঙ্গে— যা ১৯৫১ সালে চৌরঙ্গি টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়। ‘প্রসঙ্গ সনৎ কর’ অংশে ‘অন্তহীন অন্বেষণ’ শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে শিল্পী প্রসঙ্গে অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের একটি জরুরি লেখা: পূর্বপ্রকাশিত হলেও শিল্পীকে জানতে বার বার পড়ার মতো। ‘উত্তর প্রত্যুত্তর’ পর্বটি আসলে শিল্পী ও সমালোচকের পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক। ‘চিঠিপত্র’ অংশটি পাঠকের বিশেষ আগ্রহ দাবি করে। পত্রলেখকের মধ্যে আছেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কানু সেনগুপ্ত, গোষ্ঠবিহারী দে, নরেশ গুহ, সুমন দত্ত, সোমনাথ হোর, কৃষ্ণা রেড্ডি, কে জি সুব্রহ্মণ্যন প্রমুখ। শিল্পীর চিত্রাবলি সম্পাদনাতেও মুনশিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে, রচনার সঙ্গে প্রদত্ত তথ্যাবলি গ্রন্থের জরুরি সম্পদ। কয়েকটি ফাঁকের মধ্যে— ‘অন্তহীন অন্বেষণ’ লেখাটির সময়কাল চিহ্নিত নয়, আর প্রুফের সামান্য ত্রুটি বাদ দিলে বইটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হয়ে থাকবে।
সনৎ কর: জীবন ও শিল্প ২
সম্পা: সৌরভ দে, দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়
২০০০.০০
দেবভাষা
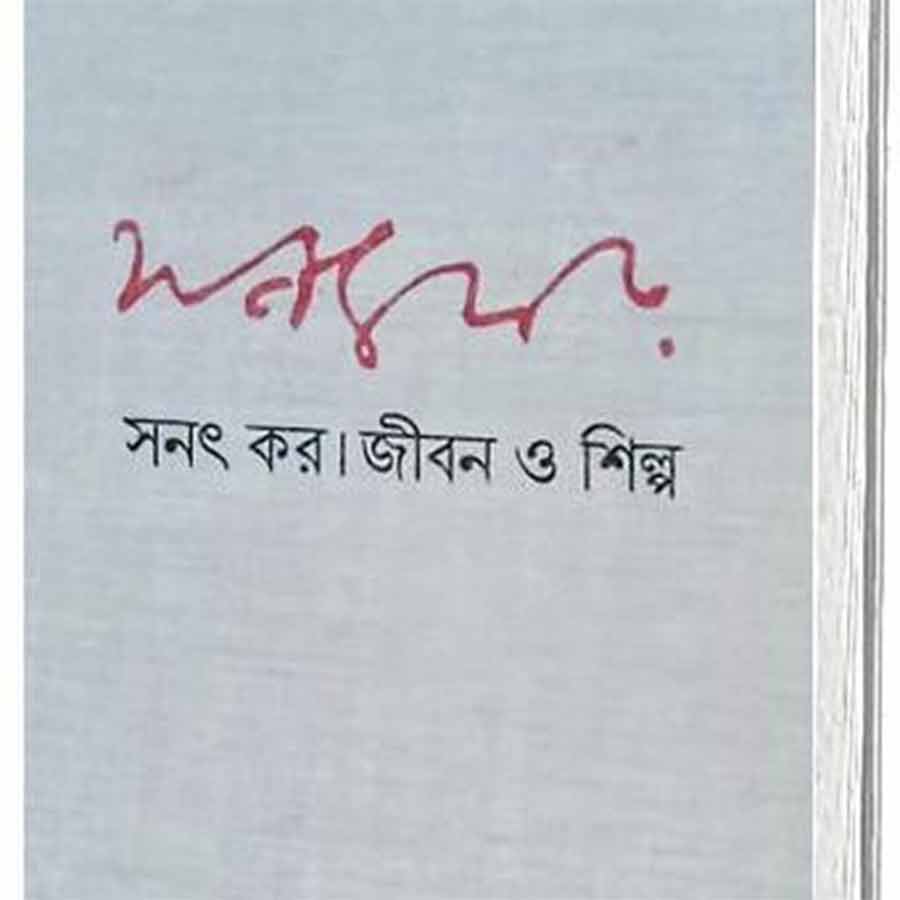
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)