কলকাতার পুজোর হিরে, চুনি, পান্নারা
কোনও পুরস্কার না-জুটলে আগে আগে মুষড়ে পড়তেন কালীদা। তবে বিচারক বা অন্য কাউকে দোষারোপ করতেন না। দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলতেন, ‘‘কী হল বলো তো!’’
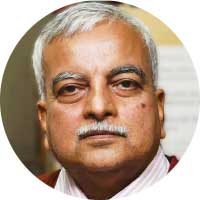
দেবদূত ঘোষঠাকুর

—প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি।
গোবিনদা
আইসিসিইউ থেকে সবে জেনারেল বেডে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ৭৬ বছরের এক বৃদ্ধ। ওয়ার্ডের জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ। পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে। বৃদ্ধের শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে দুই ব্যক্তি— এক জন মধ্যবয়সী, অন্য জন যুবা। দু’জনের বাড়িই উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেনে। দু’জনেই বৃদ্ধের প্রতিবেশী।
বৃদ্ধের মুখে এক চিলতে হাসি। বাইরের দিকে তাকিয়ে তাঁর সম্ভবত আসন্ন শারদোৎসবের কথা মনে পড়ে গেল। যুবার হাতটি ধরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘পুজো আয়োজনের সব ঠিক আছে তো? আমি ছেলেকে সব বলে রেখেছি। আমি থাকি, না-থাকি, পুজোয় যেন কোনও কিছুর অভাব না হয়।’’ বৃদ্ধের চোখ দিয়ে দু’ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সামনে দাঁড়ানো দুই প্রজন্মের দুই পুজো পাগল, অন্য প্রজন্মের এক পুজো পাগলের চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।
কালীদা (কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য), সৌমেন (সৌমেন দত্ত) আর গোবিনদা (গোবিন্দদা আর গোবিন্দদাদু থেকে গোবিনদা, গোবিন্দরাম চৌধুরী)। প্রথম জনের বয়স তখন ছিল ৬৫, দ্বিতীয় জনের ৩৫ আর তৃতীয় জনের ৭৬। গোবিনদাদের তিন পুরুষের বাস কাশী বোস লেনের বাড়িতে। যে পার্কে এখন কাশী বোস দেশের পুজোটা হয় সেই পার্কের সদর দরজার মুখোমুখি বাড়িটাই গোবিনদার। বাড়ির সামনেটা দেখে ভিতরের পরিসর সম্পর্কে কোনও ধারণা করা যাবে না। ভিতরে বিশাল উঠোন। উঠোনের চার দিকে বিশাল বিশাল পিলারের উপরে দাঁড়িয়ে আছে চারতলা বাড়ি।
নীচের উঠোনটা এতটাই বড় যে সেখানে অনায়াসে পুজো হতে পারে। হয়েওছিল এক বার। নকশাল আমলে, ১৯৭১ সালে। নকশালদের হুমকিতে পার্কে সে বার পুজো করা যায়নি। পুজো বন্ধ হয় হয়, এগিয়ে এলেন গোবিনদা। পুজোকে নিজের বাড়ির চৌহদ্দিতে তুলে নিয়ে এলেন। বুক দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি পুজোর সভাপতি। আর সম্পাদক কালীদা। নকশালদের হুমকি উপেক্ষা করে পুজো করার ‘শাস্তি’ হিসেবে কালীদা পায়ে গুলি খেয়েছিলেন। এ গল্প আমার গোবিনদার মুখ থেকে শোনা।
বাড়ির উল্টো দিকেই পুজো। সেই পুজোর সঙ্গে একাত্ম হওয়া শুরু ১২ বছর বয়সে। ‘‘পুজোর স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজটা সেফ্টিপিন দিয়ে যে দিন জামার পকেটে গাঁথলাম, সে দিন থেকেই মনে হল পুজোটা আমার। ওই ব্যাজটার উপরে খুব লোভ ছিল আমার,’’— বলতেন গোবিনদা। অবাঙালি ব্যবসায়ী পরিবার। সাধারণত এ ক্ষেত্রে ব্যবসায় বেশি জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুজো-টুজো মাথায় উঠে যায়। গোবিনদাদের কাপড়ের ব্যবসা। বড়বাজারে গদি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়লেন গোবিন্দরাম চৌধুরী। কিন্তু মা দুর্গা বোধহয় অন্য কিছু চেয়েছিলেন। তাই ওই ব্যবসার মধ্যে সেই পুজোকেই খুঁজে পেলেন আমাদের গোবিনদা।
‘‘তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুনলাম ওঁরা প্রতিমার চালচিত্র তৈরি করেন। ওঁরা আমাকে বেশ কয়েকটা দেখালেন। আমার মাথায় নকশা কিলবিল করতে লাগল। নতুন একটা কিছু করার নেশায় মেতে উঠলাম,’’— কী ভাবে তিনি ধীরে ধীরে পুজোর সঙ্গে মিশে গেলেন সেই কথা শোনাচ্ছিলেন বৃদ্ধ মানুষটি।
পাড়ার পুজোর সঙ্গে কতটা জড়িয়ে ছিলেন গোবিনদা?
এক দিন দুপুরে অফিসে বসে কাজ করছি। সৌমেনের ফোন এল, ‘‘জরুরি দরকার। গোবিনদা তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন। আজ বিকেলেই এসো।’’ আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফোনটা রেখে দিল।
তখনও গোবিনদাকে চিনতাম না। সৌমেনের ফোনটা পেয়ে ভাবছিলাম, কে এই গোবিনদা? কোনও রাজনৈতিক নেতা? উঁহু! শিল্পপতি বা বিশাল ব্যবসায়ী? তা-ও নয়। শিল্পী, অভিনেতা? মিলল না। সাক্ষাৎ হতেই দেখলাম, উনি একজন ছাপোষা মানুষ। বড়বাজারে গদি আছে। মাতৃভাষা হিন্দি। হাত দুটো ধরে বললেন, ‘‘এই পুজোটা আমার প্রাণ। মরার আগে দেখে যেতে চাই, মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ছে মণ্ডপে, সারা দিন, সারা রাত লোক আসছে। আমার এই নাতিরা রাতের পর রাত ভিড় সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। আমি বারান্দায় বসে সেই ভিড় দেখছি। কখন যে সকাল হয়ে গিয়েছে তা বুঝতেই পারছি না।’’ ওঁর বিশ্বাস ছিল, আমিই নাকি পারি ভিড়ের অভিমুখটা কাশী বোস লেনে ঘোরাতে।
আমাদের ওই সাক্ষাতের পরে সাত বছর বেঁচেছিলেন গোবিনদা। তাঁর আশা পূরণ হয়েছিল। পুরস্কার রাখার জায়গা ছিল না তাঁর ওই ছোট্ট ঘরে। পুজোর চার দিন অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দাতেই বসে থাকতেন আমাদের গোবিনদা।
তিনি চলে গিয়েছেন। কাশী বোস লেনের পুজোর নিয়ম বদলায়নি এতটুকুও। পাশ দিয়ে গেলেই গোবিনদার গলা পাই, ‘‘আমি থাকি, না-থাকি, পুজোয় যেন কোনও কিছুর অভাব না হয়।’’
কালীদা
ফোনটা আসা শুরু হত ঠিক এপ্রিল মাস থেকে। যে দিন পুজোর শিল্পীর সঙ্গে বায়নাপত্র সব পাকা হয়ে যেত, সে দিন। আর নিয়ম করে ফোন চলত বিজয়া দশমী পর্যন্ত। প্রথমে মাসে এক বার করে। পুজো যত এগিয়ে আসত, বাড়ত ফোনের সংখ্যাও।
যবে থেকে পুজোর লেখালেখি শুরু করেছি, খিদিরপুর থেকে ওই ফোন আসার শুরু। তার পরে আরও ২৫ বছর পুজোর লেখার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ফোন বন্ধ হয়নি এক বারের জন্য।
অনেক পুরনো বাঙালি হিন্দু পরিবারের মতো খিদিরপুরের বাস তুলে ওঁরা উঠে গিয়েছেন বেহালায়। কিন্তু খিদিরপুরের ওই পুজোটি তাঁকে ছাড়েনি। ওই পুজোর কর্মকর্তা পাল্টায়, শিল্পী বদলায়, পুজোর ধরন বদলায়। এ সব নিয়ে মনান্তরে অনেকে দূরে সরে যান।
কিন্তু ওই ফোনটা আসা বন্ধ হয়নি।
খিদিরপুরের মতো জায়গায় ওই পুজোর অস্তিত্ব যে এখনও রয়েছে, ওই ফোনটা তা জানান দিত। আমাদের ওই ফোনবন্ধু কালীদা (কালী সাহা) জনসংযোগে কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয়।
বাজারে নতুন ইলিশ মাছ উঠেছে। সাত সকালে ফোন, ‘‘দেবদূত বাড়ি আছো? ঝুমার (আমার স্ত্রীর ডাক নাম) জন্য একটা ইলিশ মাছ কিনেছি। দিয়ে আসব বাড়িতে।’’ আমি ফোনটা দিয়ে দিতাম স্ত্রীকে। অফিসের পথে স্ত্রীর ফোন, ‘‘এই এত্ত বড় একটা ইলিশ মাছ নিজে এসে দিয়ে গিয়েছেন।’’
বাচ্চাদের হাতের কাজ শেখানোর ক্লাস নিতেন উনি।
একটা সময় সেই কাজের নিদর্শন নিয়ে হাজির হতেন অফিসে। শুধু আমার জন্য নয়। অফিসে যে সব রিপোর্টার, ফোটোগ্রাফার কিংবা সাব এডিটর পুজোর লেখালেখি, ছবি তোলা কিংবা পাতা তৈরির কাজ করতেন প্রত্যেকের নামে নামে আনতেন উপহার। কখনও মোমের তৈরি, কখনও বা কাগজের তৈরি ঘর সাজানোর উপকরণ।
আর পুজোর আগে ঠিক ওই কয়েক জনের নামে পৌঁছে যেত খাম। পুজোর ভিআইপি পাশ। অষ্টমী কিংবা নবমীতে আসত ভোগ। নিয়ম করে। শুধু আগে একটা ফোন করে নিতেন।
ওই পুজোর ব্যাপারে সাক্ষাৎকারে অন্য কারও নাম বেরোত। কখনও শুধুই প্রতিমা বা মণ্ডপের ছবি। সংশ্লিষ্ট সকলকে ফোন করে ধন্যবাদ জানাতেন। পুজোর ব্র্যান্ডিং কী ভাবে করতে হয় তা দেখিয়ে গিয়েছেন মানুষটা।
রাজনৈতিক দল নয়, কর্পোরেট কর্তা নন— স্রেফ পুজো আর ক্লাবকে ভালবাসেন বলেই সারা বছর মাথায় নানা পরিকল্পনা ঘোরে। আগে অনাথ শিশু, বৃদ্ধাবাসের বাসিন্দাদের জন্য কিছু না কিছু করতেন, যাতে ক্লাবের পরিচিতি বাড়ে। সেই পরিকল্পনা হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে একটা সময়। নতুন ছকে দুর্গাবাহিনীকে রাস্তায় নামিয়ে চমক দিয়েছেন।
কালের নিয়মে বয়স বাড়বেই। ওঁরও বেড়েছে। অফিসে আসাটা কিছুটা কমেছিল। কমেছিল বেহালার শীলপাড়া থেকে খিদিরপুর নিত্য আসা-যাওয়া। পরিবারের লোকেরা আটকাতেন। কিন্তু পুজো এলেই ফোন কানে অতি সক্রিয়। তাঁকে ঠেকানো যেত না। পিংপং বলের মতো বেহালা আর খিদিরপুর ছুটে বেড়ান ওই প্রবীণ মানুষটা। ঘনিষ্ঠেরা রসিকতা করে বলতেন, ‘‘বয়সটাই বেড়েছে। ভিতরে একেবারে শিশু। ওর নাতির মতো।’’ আমি অনেক সময় কপট রাগ দেখিয়ে বলতাম, ‘‘ছাড়ুন তো মশাই! আপনাদের মতো এ রকম পুজো কলকাতায় হাজারটা আছে। কেন গুরুত্ব পাবে আপনার পুজো!’’ কিছুটা দমে উনি বলতেন, ‘‘আমাকে যা খুশি বল, শিল্পীকে গালাগাল দাও, কিন্তু দেখো আমাদের পুজোটা যেন…।’’
কোনও পুরস্কার না-জুটলে আগে আগে মুষড়ে পড়তেন কালীদা। তবে বিচারক বা অন্য কাউকে দোষারোপ করতেন না। দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলতেন, ‘‘কী হল বলো তো!’’
দুঃখের দিনে শুধু ফোনটা আমাকে করতেন। আর সুখের দিনে ধরে ধরে সবাইকে। পরের দিকে অবশ্য পুরস্কার না-পাওয়াটাই দস্তুর হয়ে গিয়েছিল। সেটা মেনেও নিয়েছিলেন মানুষটা। নিয়ম করে বিজয়া দশমীর দিন শুভেচ্ছা জানাতেন। এ রকম সবাইকে ভালবাসার মানুষ, সবার কাছে ভালবাসা পাওয়ার মানুষ আর মিলছে কই?
গুরু
ওঁর সঙ্গে সারা বছরই দেখা হত কোনও না-কোনও ভাবে।
কেওড়াতলা মহাশ্মশানে কারও সৎকারে গেলে একটা ফোন করে দিতাম। গিয়ে দেখতাম দলবল নিয়ে উনি হাজির। কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই সৎকার পর্ব শেষ হত। শুধু তাই নয়, সকলের হাতে হাতে পৌঁছে যেত চা-ভর্তি কাপ, বিস্কুট। আমাকে কিছু করতেই হত না। সৎকার শেষে হাতে পৌঁছে যেত ডেথ সার্টিফিকেট।
আমরা কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকতাম না। দু’তরফের সম্বোধন ছিল ‘গুরু’। ধর্মতলার দিকে গেলেই ফোন করতেন, ‘‘গুরু দেখা হবে নাকি? ও দিকেই যাচ্ছি।’’ কখনও ফোন করে বলতেন, ‘‘গুরু নতুন একটা নাটক নামাচ্ছি তপন থিয়েটারে। রিভিউয়ের জন্য একটা কার্ড দিয়ে যাব।’’ উনি আসতেন। এক কাপ কফি খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করতেন। একটা কার্ড নাটক রিভিউ বিভাগে পাঠিয়ে দিতাম (যদিও জানতাম ছাপা হবে না) আর একটা কার্ড নাট্যপ্রেমী কাউকে দিতাম। জানতাম আনন্দবাজার কাউকে না-পাঠালেও, আমার পাঠানো নাট্যপ্রেমী ঠিক যাবেনই। কাগজে রিভিউ ছাপা হোক বা না-হোক দুই ‘গুরু’র সম্পর্কে তা কোনও প্রভাব ফেলত না।
আমি এ বার লিখছি কালীঘাটের নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিটের ৬৬ পল্লির পুজোর রজত সেনগুপ্তের কথা। এক্কেবারে সাদা মনের মানুষ। সোজা কথা সোজা ভাবে বলতেন। আমার সঙ্গে তাই মিল খেত। অনেক কথাই বলতেন যেগুলি প্রকাশ্যে এলে ঘোর বিতর্ক বাঁধতে পারে। আমি কখনও তা প্রকাশ করিনি। করবও না। তবে কী ভাবে আমার উদ্যোগে বড়িশার একই রাস্তার উপরে থাকা দু’টি পুজো মিলে গিয়েছিল, সেই গল্পটা বার বার শুনতেন। আমি মাঝে মাঝেই বলতাম, ‘‘তোমার এই এক গলিতে তিনটে পুজোকে এক করে দিতে পার না?’’ মাথা নাড়তেন। তার পরে সখের বাজারের দু’টি ক্লাব কী ভাবে মিলে গেল সেই গল্পটা শুনতে চাইতেন। নিজের ইচ্ছেটা কখনও প্রকাশ করেননি।
নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিটের ওই গলিটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে মনটা কেমন হুহু করে ওঠে। সদানন্দ রোডের এক দিকে নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট, অন্য দিকে তপন থিয়েটার। পুজো আর থিয়েটার— দুটোই ছিল রজতদার বেঁচে থাকার দুই উপকরণ। সদানন্দ রোডটা এ ক’মাস এড়িয়ে চলেছি। কানে শুধু ‘গুরু’ শব্দটা বাজছে।
রজতদা নেই। ৬৬ পল্লির ওই গলিটায় এ বার পুজোয় যেতে পারব তো? রঞ্জিতদা অর্থাৎ রঞ্জিত ভট্টাচার্য মারা যাওয়া ইস্তক পার্ক সার্কাস ময়দানের পুজোয় আর যাইনি। আমার হাত ধরে সারা মণ্ডপ ঘুরে বেড়ানো, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটা রঞ্জিতদা প্রতি বছর করতেন। বৎসরান্তে একই লোকের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হতে হত। অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু রঞ্জিতদার ‘ছেলেমানুষি’কে অপমান করতে পারিনি। তাই রঞ্জিতদা চলে যাওয়ার পরে আর ও দিকে মাড়াইনি।
রজতদা নেই। ৬৬ পল্লির ওই গলিটায় পুজোয় আর যেতে পারব তো?
নাথদা
চাকরি করতেন উচ্চ পদে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক বড়কর্তা। মোটা বেতন। অবসরের বছর দশেক আগে মাথায় যে কী ভূত চাপল কে জানে!
ক্লাবের মধ্যে কোনও ভাবে একটা পুজো হত। নমো নমো করে। সন্ধ্যার পরে গুটিকয়েক লোক মণ্ডপ আগলে বসে থাকেন। রাতে কে থাকবে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। রাত কখন শেষ হবে তার জন্য শুরু হয় অন্তহীন প্রতীক্ষা। এক-দেড় কিলোমিটারের মধ্যে পরিস্থিতিটা পুরো আলাদা। সেখানে রাতভর মানুষের আনাগোনা। রাত তিনটেতেও লম্বা লাইন। রাত কখন শেষ হয়ে যায়, বোঝাই যায় না।
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক বড়কর্তা কয়েক জনকে নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত নিজের পাড়ার পুজোর মণ্ডপের সামনে চেয়ার পেতে বসে থাকেন। আর স্বপ্ন দেখেন, রাত বাড়ছে আর তাঁদের ওই মণ্ডপে আছড়ে পড়ছে জনস্রোত। পুলিশকর্তারা ছোটাছুটি করছেন। খাবারের দোকানগুলিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। টিভি চ্যানেল আসছে। বাইট নিয়ে যাচ্ছে। সকালে বাড়ি ফিরছেন বটে, কিন্তু স্নান করে খেয়েই ফের চলে আসতে হচ্ছে মণ্ডপে।
ওই স্বপ্ন সফল করার ভূত এ বার চেপে বসল ওই ব্যাঙ্ককর্তার মাথায়। আর সঙ্গে পেয়ে গেলেন দুই পুজো-পাগল ভাইকে। দু’জনেই কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার। জুটে গেলেন আরও কয়েক জন। তাঁদের গৃহিনীরাও অতি উৎসাহী। তৈরি হল নতুন কমিটি। ক্লাব ছেড়ে মণ্ডপ নেমে এল বাইরে। রামলালবাজার সর্বজনীনও নাম লেখাল থিমের পুজোয়। কলকাতার নামী থিমশিল্পীরা একে একে এসে জুটলেন। ব্যাঙ্ক অফিসার রবীন্দ্রকিশোর নাথের স্বপ্ন সফল হল। অনুপম মজুমদার, কবীর মজুমদার, তাপস গুহদের পুজোর এক মাস আগে থেকেই রাতের ঘুম গেল ছুটে। ওদের অনেকেরই পুজোর ক’দিন সারা রাত সপরিবারে শহর ঘুরে ঠাকুর দেখার অভ্যাস ছিল। সেই অভ্যাসও গেল ছুটে। তাতে পারিবারিক অশান্তি হল না মোটেই। কারণ, বাড়ির সব সদস্যই যে স্বেচ্ছাসেবক! সবার ডিউটি ভাগ করা থাকে। বাড়িতে আসাটা আসলে নিয়ম রক্ষার। দু’মুঠো মুখে তোলার জন্য!
পুজোর প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রকিশোরের অবসরের দিন এক সময় চলে এল। আসলে ওই ব্যাঙ্ককর্তাই পুজোর খরচ-খরচার একটা বড় অংশ বহন করতেন। তাই চিন্তিত সবাই। এ বার কি তা হলে জৌলুস হারাবে রামলালবাজারের পুজো? আবার কি পুজো ঢুকে যাবে ক্লাবের চার দেওয়ালের মধ্যে?
রবীন্দ্রকিশোর (সবার নাথদা) কিন্তু অন্য রকম ভাবছিলেন। কী ভাবছিলেন সেটা তাঁর পরিবারের লোকেরাও জানতেন না। দুই মেয়ে চাকরি করেন। নিজে মোটা টাকার পেনশন পান। কাজেই অবসরকালীন জীবনে কোনও চাপ ছিল না। কিন্তু পুজোয় যে টাকাটা তিনি সংগ্রহ করে দিতেন তার সংস্থান হবে কী করে? এক দিন সন্ধ্যায় ক্লাবের সভায় রবীন্দ্রকিশোর নিজের পরিকল্পনা ফাঁস করলেন, ‘‘পুজো যেমন চলছে তেমনই চলবে। আমি যে টাকাটার ব্যবস্থা করে দিতাম, সেটাই দেব। পুজোর আনন্দে কোনও বাধা যেন না পড়ে।’’ তার দু’দিন আগেই অফিস থেকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর চাকরির মেয়াদ যে কোনও ভাবেই বাড়ছে না, সেটা নিশ্চিত। তা হলে টাকাটা তিনি দেবেন কী করে? নাথবৌদি ওই সভায় হাজির। তিনিও মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছেন না। মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!
এ বার বোমাটা ফাটালেন নাথদা, ‘‘আমি একটা চাকরি নিয়েছি। অন্ধ্রপ্রদেশে। বিজয়ওয়াড়ার কাছে। আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ওরাই করবে।’’ নাথবৌদি চমকে উঠলেন। এই বয়েসে বিদেশ-বিভুঁইয়ে গিয়ে হাত পুড়িয়ে খাবে নাকি লোকটা? এ সবের কোনও দরকার ছিল কি? নাথদা বললেন, ‘‘আমার এই নতুন চাকরিটার মূল্য আমার কাছে অপরিসীম।’’
পরের রবিবার নাথদা এলেন আমার বাড়িতে। সঙ্গে সেই অনুপম। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘ব্যাপারটা কী হল বলুন তো!’’ নাথদা হেসে বললেন, ‘‘বাইরে বাইরে অনেক থেকেছি। আমার কোনও অসুবিধা হবে না। একটাই আনন্দ পুজোটা বেঁচে যাবে।’’ সারা বছর ছুটি নেই। পুজোর সময় টানা দু’মাসের ছুটি দিতে হবে। এটাই ছিল নাথদার একমাত্র শর্ত। নাথদার জীবনে শুরুই হল নতুন পর্ব। আর দৌড় থামল না রামলালবাজার সর্বজনীনের।
মানুষ ভাবে এক। আর হয় অন্য কিছু। ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হল। তত দিনে রামলালবাজার পুজো কমিটির তহবিলের স্বাস্থ্য ফিরেছে। সেই তহবিলের দিকে নজর ছিল অনেকের। রাজ্যে পট পরিবর্তনের ফলে তাদেরই সব থেকে সুবিধা হয়ে গেল। নানা ভাবে হেনস্থা করা শুরু হল নাথদাদের। রাজনীতির কারবারীদের সঙ্গে নাথদারা পেরে উঠবেন কী করে? এক রকম জোর করেই পুজোর দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিল নতুন কমিটি। তার জেরে গত ১০ বছরে রামলালবাজারের পুজোটা ফের সেঁধিয়ে গেল ক্লাবের চার দেওয়ালের মধ্যে। নাথদার চাকরি করার প্রয়োজন থাকল না আর। ঘরের ছেলে ফিরে এলেন ঘরে।
নাথদার সেকেন্ড ইন কমান্ড অনুপম কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনি আয়কর দফতরের বন্ধুদের নিয়ে একটি পুজো পুরস্কারের সূচনা করে ফেললেন ওই বছরই। নাথদাদের পুরো দলটাই যুক্ত হয়ে গেল তার সঙ্গে। ওই পুজো পুরস্কারের সদর দফতর হল রামলালবাজারেই। পুজো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেলেন নাথদা। তিনি তখন আর শুধু রামলালবাজারের নন। প্রকৃত অর্থেই তিনি তখন সর্বজনীন।






