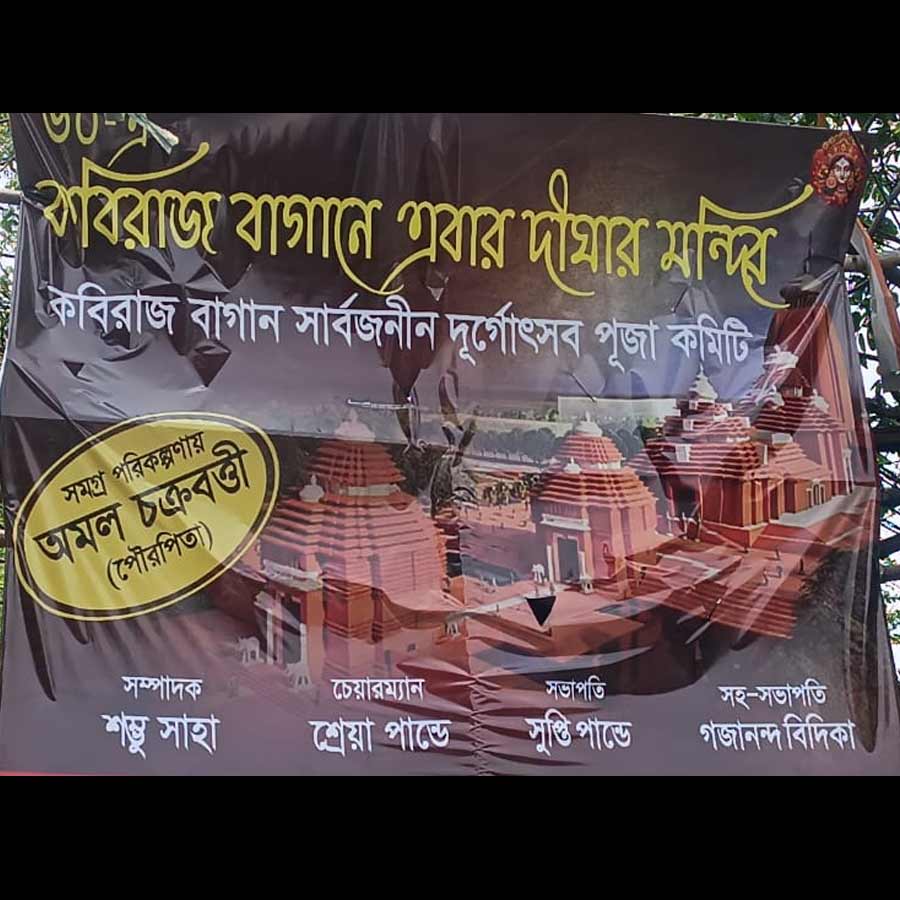এই রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যস্ততার বাইরে এক জন ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্তরিক অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর নীরবতা আমাদের মতো নাট্যকর্মীদের দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ হয়ে আছে। বাঙালির থিয়েটার বিষয়ে তিনি বড় একটা কথা বলেন না। সরকারি নাট্য-অনুষ্ঠানের আসরে, নাট্যমেলায় বা নাট্য-প্রদর্শনীতে তাঁর অংশগ্রহণ কদাচিৎ চোখে পড়ে। সেই জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন আগে থিয়েটার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন দেখে নাট্যকর্মী হিসাবে ভাল লাগল। ইংরেজি নববর্ষের সূচনায় হাতিবাগানে ‘স্টার থিয়েটার’ নাম পরিবর্তন করে হবে ‘বিনোদিনী থিয়েটার’। এই ঘোষণা এসেছিল জনসভায় করা তাঁর প্রকাশ্য বয়ানে।
সত্যি বলতে কী, এক দিক থেকে দেখলে দীর্ঘ দিনের ত্রুটি শোধনের দিকে এটি একটি ইতিমূলক পদক্ষেপ। থিয়েটারের ঐতিহ্যবাহী আমাদের এই কলকাতা শহরে বড় নাট্যগৃহগুলি সবই পুরুষ নাট্যপ্রতিভাদের নাম বহন করছে। মাইকেল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিশির বা অহীন্দ্র-র পাশে এ বার বিনোদিনীর নামও বহন করবে একটি নাট্যগৃহ, এ তো সঙ্গত আনন্দের বিষয়। যদিও যে ‘স্টার থিয়েটার’কে ঘিরে বিনোদিনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কালজয়ী আখ্যান জড়িয়ে আছে, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমনকি বাংলা থিয়েটারের আদি স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র, সেই ‘স্টার থিয়েটার’ বহু দিন আগেই ভাঙা পড়েছে শহরের সম্প্রসারণের দাবিতে। তবু এহ বাহ্য! হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয় যখন দেখি, যে নাট্যমঞ্চের নতুন নামকরণ হল, সেই গৃহে আর নাট্যাভিনয় হয় না। হয় জনপ্রিয় বাংলা বা হিন্দি সিনেমার প্রদর্শনী।
‘স্টার থিয়েটার’-এর তো তবু বাইরের আদলটুকু আছে, ‘রঙমহল’ বা ‘বিশ্বরূপা’-র তো তাও নেই। বহুতল বাড়ি বা বিশাল বাজারে পরিণত হয়েছে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার-সহ কিংবদন্তি নাট্যপ্রতিভাদের স্মৃতিবিজড়িত এই সব নাট্যগৃহ। পরবর্তী কালের ‘রঙ্গনা থিয়েটার’ বা ‘সারকারিনা নাট্যমঞ্চ’রও শুধু ইমারতটুকু আছে, ভিতরে অবলুপ্তির অন্ধকার। ‘বিজন থিয়েটার’-এর বোধ হয় বাড়িটুকুও নেই। একমাত্র ‘মিনার্ভা থিয়েটার’ বাম আমলেই সরকারি হস্তক্ষেপে অন্য রকমের এক ভূমিকায় বেঁচে আছে। এই জমানাতেও মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের কর্মস্থল হিসাবেই মূলত ব্যবহৃত হচ্ছে মিনার্ভা। বাঙালির গর্বের এই সাধারণ রঙ্গালয়ের অবলুপ্তির যবনিকা নেমে আসে গত শতাব্দীর শেষে। একে বাঁচানোর অসম লড়াইয়ে একা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও শেষ পর্যন্ত হতোদ্যম হলে নিবে যায় পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয়ের শেষ প্রদীপ। তখনকার বামপন্থী সরকার এবং শিল্পী-কলাকুশলী-বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল নিষ্ক্রিয়, নীরব। তার পরে সিকি শতাব্দী কেটে গেছে। আজ যাঁরা ক্ষমতায়, তাঁদেরও এ নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। সমাজের কোনও স্তরে কোথাও এই সাধারণ রঙ্গালয়ের অবলুপ্তি নিয়ে কোনও অভাববোধ বা আক্ষেপের কথা শোনা যায় না। তাই আজ হঠাৎ সেই ভাঙা দেউলে ঝান্ডা পুঁতে নতুন নামকরণের উদ্যোগ করুণ পরিহাসের মতো ঠেকে।
হাতিবাগানের পেশাদারি থিয়েটারের ক্ষয় ও ভাঙন এবং অবশেষে তার বিনাশের কারণ অনুসন্ধানে তথ্যনির্ভর কোনও সিরিয়াস তদন্ত হতে দেখিনি। সেটা হওয়া দরকার। খুবই দরকার। কারণ, যে থিয়েটার এখন বেঁচে আছে এ রাজ্যে, তার কোনও পেশাদার পরিকাঠামো নেই। ভাল থিয়েটারের পেশাদারি ভিত্তিতৈরি করতে না পারলে যেটুকু থিয়েটার কিছু নাট্যদলের অসংগঠিত পাগলামির উপর নির্ভর করে চলছে এখনও, দমকা হাওয়ায় তার আলোটুকুও নিবে যেতে কত ক্ষণ!
বাঙালির থিয়েটারের যে ক্ষীয়মাণ ধারাটুকু আজও বহমান, তার গায়ে ‘গ্রুপ থিয়েটার’ নামক বিদেশি শব্দবন্ধের লেবেল কে বা কারা কবে লাগিয়ে দিয়েছিল জানি না। গত শতকের চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন বা পরের যুগের নবনাট্যের চালিকাশক্তিগুলি, সেই আদর্শ নীতি বা উদ্দেশ্যগুলি আজকালের প্রহারে বিলুপ্ত। বামপন্থার বিকাশ ও প্রসারের আন্দোলনের সঙ্গে নাড়ি বাঁধা ছিল এ রাজ্যের প্রতিবাদী রাজনৈতিক থিয়েটারের। আজ বামপন্থার অস্তিত্বের সঙ্কটের আবহে সেই থিয়েটারের পালে হাওয়া নেই। পাশাপাশি নাটকের দলগুলির আভ্যন্তরিক গঠনে এসেছে এবং আসছে বিপুল বদল। চার দিকের সমাজ-রাজনীতিতে যে নৈরাজ্য চলছে, তারই ধাক্কা অনিবার্য ভাবে এসে পড়ছে থিয়েটারেও। এক-একটি সংগঠন এক-একটি মোর্চা বা পাটাতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিল্পী-কলাকুশলীর সঙ্গে সঙ্গে এখন এদের নির্দেশকও পাল্টে যাচ্ছে ঋতুতে ঋতুতে। ফলত, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা নীতি বা এমনকি কোনও মৌল প্রত্যয়কে সামনে রেখে থিয়েটার করার সাবেক রীতি আজ প্রায় বিস্মৃত। ব্যতিক্রম যে নেই তা বলব না। তবে তা যেন নিয়মকেই প্রমাণ করার জন্য।
এই এলোমেলো অবস্থাতেও এই নতুন শতাব্দীর গত দু’দশকের বাংলা থিয়েটারে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ যে হতে পেরেছে এটাই আশ্চর্যের। তিন-চারটি প্রজন্মের নাট্যস্রষ্টারা পাশাপাশি কাজ করে চলেছেন, এমন সুস্থ দৃষ্টান্তও উজ্জীবিত করেছে। অতিমারির ঝাপট কাটিয়ে গত পাঁচ বছরের থিয়েটার আবার পায়ের তলার জমি খুঁজছে। উৎপল দত্তের অনেক শক্তিশালী নাটকের পুনরভিনয় ঘটতে দেখেছি এ যুগের নানা নির্দেশকের হাতে। মনে হয়েছে যেন প্রতিবাদী রাজনৈতিক থিয়েটার দিকচিহ্ন খুঁজতে চাইছে গত শতাব্দীর ক্লাসিকের হাত ধরে। পুনরভিনয় শুরু হয়েছে মনোজ মিত্রের নাটকেরও। তবে এতে করে যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে নতুন শক্তিশালী নাটককারের অনুপস্থিতির কথাও। মনে রাখতে হবে, মহিলা নাট্যপরিচালকদের জোরালো আবির্ভাবের কথা। মনে রাখতে হবে, মহানগরীর সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর জেলাগুলিতেও মফস্সল শহরে গড়ে উঠছে স্থানীয় নাট্যকেন্দ্র। আজও অনেক স্বপ্ন নিয়ে নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হচ্ছে সেখানে, এ আমি চাক্ষুষ করেছি বার বার।
গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা এই অসংগঠিত থিয়েটারের প্রাণপ্রদীপগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্র বা/এবং সমাজের সদিচ্ছা, সহযোগ, আনুকূল্য চাই। প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য আধিপত্যের যুগে আজ সিনেমাই বিপন্ন শিল্পের তালিকায় চলে গেছে। সেখানে থিয়েটার তো কোন ছার! তবু সমস্ত সভ্য দেশে প্রশাসন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি থিয়েটারকে বাঁচানোর দায়িত্ব নেয়। একটা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের যে সব সূচক আছে, তার মধ্যে নাট্যমঞ্চ একটি বড় জায়গা পায়। কিন্তু এ দেশে কেন্দ্র-রাজ্য কোথাও সরকারি স্তরে এ বিষয়ে কোনও অবহিতি নেই। অবহেলার এই ঐতিহ্য সমানে চলছে। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯৫১ সালে শ্রীরঙ্গমে ষোড়শী-র অভিনয় দেখে মুগ্ধ রুশ নাট্য-কিংবদন্তি চেরকাসভ ও পুডভকিন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে বলেন, আপনি তো বিশাল প্রতিভাবান! আমাদের গুরু স্তানিস্লাভস্কির চেয়ে কোনও অংশে খাটো নন আপনি। আপনাকে কেন এই জীর্ণ মঞ্চে দরিদ্র থিয়েটারে কাজ করতে হয়! উত্তরে শিশিরকুমার বলেন, এই আমার ভবিতব্য। “ইন ইয়োর কান্ট্রি দ্য স্টেট উইল লেন্ড সাপোর্ট টু দ্য স্টেজ... উই মাস্ট স্ট্যান্ড অন আওয়ার ওন ফিট।”
তার পর পঁচাত্তর বছর কেটে গেছে। থিয়েটারের মানুষদের একই ভবিতব্য: নিজেদের দাঁড়ানোর জায়গা নিজেদের করে নিতে হবে। কেউ কোনও সাহায্যের হাত এগিয়ে দেবে না। তাই ‘স্টার থিয়েটার’-এর নাম পাল্টাবে, কিন্তু সেই মঞ্চে নট-নটীদের পায়ের আওয়াজ বা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের কলধ্বনি আর শোনা যাবে না।
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)