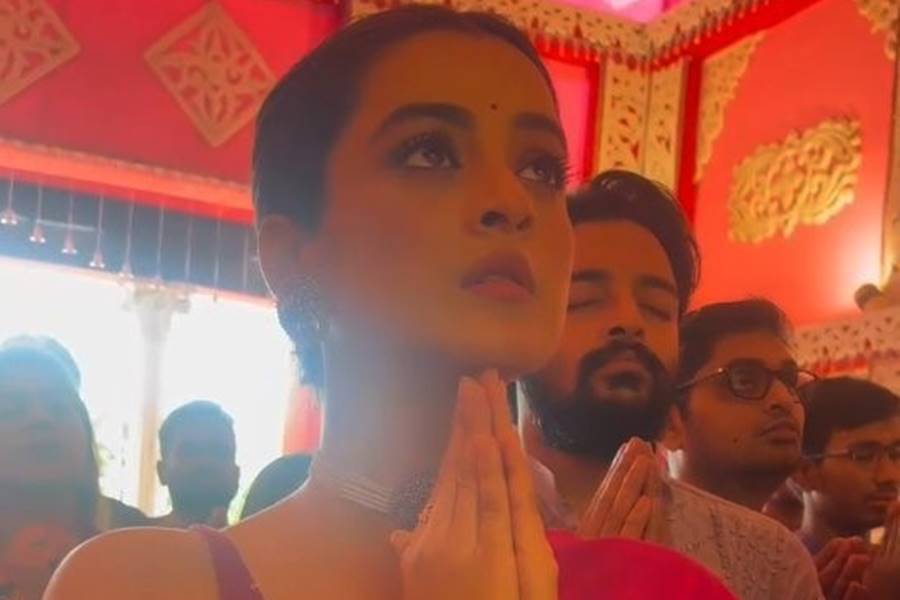সম্পাদক সমীপেষু: নিন্দার সাহস
রাজ্যের প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সরব। ভাল কথা। কিন্তু মৌলবাদের একটা দিকের বিরুদ্ধতা করতে দিয়ে তার আরও ভয়ঙ্কর দিকের বিরোধিতায় তাঁদের মন সায় দেয় না।

—ফাইল চিত্র।
সেমন্তী ঘোষ তাঁর ‘বর্বর জয়ের উল্লাসে’ (৩-১১) প্রবন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: “ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘুদের অন্যায়কে ‘ছোট’ করে দেখার যে বামঘেঁষা প্রবণতা, তা ধর্মান্ধতার মতোই বিপজ্জনক।” যে কোনও উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা নিন্দনীয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে স্বার্থপূর্ণ নির্বাচনী দ্বন্দ্বে জয়লাভের আশায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বিশেষ ভাবে নিয়োজিত করা হয়। অনস্বীকার্য, স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ইসলামি সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে নীরব থাকাই লাভজনক মনে করে। এবং সংখ্যালঘুর প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব দোষের মনে করে না।
রাজ্যের প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সরব। ভাল কথা। কিন্তু মৌলবাদের একটা দিকের বিরুদ্ধতা করতে দিয়ে তার আরও ভয়ঙ্কর দিকের বিরোধিতায় তাঁদের মন সায় দেয় না। কেন? এর উত্তর দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। কবি জয়দেব বসুকে দেওয়া চিঠিতে তিনি লিখেছেন: “বস্তুত আমরা ভয় পাই। ভয় পাই যে তাহলেই হয়তো আমরা সাম্প্রদায়িক নামে চিহ্নিত হয়ে যাব, ভয় পাই যে তাহলেই হয়তো সংখ্যালঘুদের বিরাগভাজন হব।” (‘লেখা যখন হয় না’, শঙ্খ ঘোষ, পৃ ১০০-১০১)। এই বিপজ্জনক প্রবণতার সুবিধা তোলে অপর কিছু রাজনৈতিক দল। উত্তেজিত হন সংখ্যাগরিষ্ঠ কিছু মানুষ।
তবে, ভারতে বহুত্বের বিনাশ সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ, অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের সনাতন ধর্মের সহনশীলতা ও গ্রহণধর্মিতার আদর্শ। ভারতে সংবিধান প্রণেতাদের কৃতিত্ব খাটো না করেও বলা যায়, যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল শিকড় হিন্দুধর্মের মূল দর্শন ও নীতিতে নিহিত। সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নানা পথকে সম্মান জানানো সনাতন হিন্দুধর্মের মজ্জাগত। প্রগতিশীল তকমায় আঘাত লাগবে বা সাম্প্রদায়িক গন্ধ আশঙ্কা করে এই সত্য অস্বীকার করা ভারতীয় রাজনীতিবিদদের এক মস্ত ভুল। বরং এই কথা দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করলে ভারতে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আরও মজবুত হত।
বহু শাখা-সমন্বিত হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বহু মানুষ অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নানা কুসংস্কারকে আঁকড়ে থাকেন। কিন্তু এই বিকৃতিগুলিকে হিন্দুধর্মের আসল রূপ বলে প্রচারে ক্ষতি আছে, লাভ নেই। এই ভুলই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে প্রগতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাশক্তি মিশ্র, কলকাতা-২৯
কমিশন-রাজ
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, প্রয়াত রাজীব গান্ধী ১৯৮৫ সালে বলেছিলেন, কেন্দ্র এক জন নাগরিকের জন্য এক টাকা উন্নয়ন ধার্য করলে নাগরিকের কাছে তার মাত্র ১৫ পয়সা পৌঁছয়! ঠিক সেই সূত্র ধরেই সুগত মারজিৎ তাঁর ‘দুর্নীতি এবং উন্নয়ন’ (১৩-১১) প্রবন্ধে বলেছেন যে, এই বাকি অর্থ উন্নয়নের স্বার্থেই ‘কমিশন’ হিসাবে ঘুরপথে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে, নয়তো উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নয়ন বলতে প্রবন্ধকার ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন! যে উদাহরণ তুলে ধরেছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, সেটি ব্যক্তিকে সরকারি অনুদান দেওয়ার প্রকল্প, উদ্দেশ্য দারিদ্র নিবারণ। এই ধরনের প্রকল্পের দু’টি পর্যায় থাকে। উপভোক্তা নির্বাচন, এবং সহায়তা প্রদান। দীর্ঘ দিন ব্লক, মহকুমা এবং জেলাস্তরে প্রশাসনিক দফতরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধি, বা তাঁদের সহযোগীদের সক্রিয় যোগদানে উপভোক্তা নির্বাচনের সময় থেকেই কী ভাবে উৎকোচ (যাকে লেখক আপাত-গ্রহণযোগ্য শব্দে প্রকাশ করেছেন, ‘কমিশন’) সংগ্রহ চলে। যিনি দেড় লক্ষ টাকা পাওয়ার জন্য কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা অগ্রিম উৎকোচ দিতে পারেন, তিনি কি প্রকৃতই উপভোক্তা হওয়ার যোগ্য? আর যিনি প্রকৃত গরিব, তিনি কি এই টাকাটা দিতে সক্ষম হবেন? সেই পথেই প্রথম পা রাখে অযোগ্য উপভোক্তার নির্বাচন। যে কারণে গত বছর কেন্দ্রের বিশেষ পরিদর্শনের পর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উপভোক্তার তালিকায় বিপুল সংখ্যক অযোগ্য উপভোক্তার নাম বাদ দিতে প্রশাসন বাধ্য হয়।
কমিশন দেওয়ার পরের দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের যুক্তি, এটাই নাকি অর্থনীতির গোড়ার কথা যে, দুর্নীতিশূন্য করলে কাজও শূন্য হবে। আমি অর্থনীতির ছাত্র নই। তবে, অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আজ থেকে বছর পাঁচ-ছয় আগে অনুদানের টাকা উপভোক্তার কাছে দিতেন পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকেরা। কাগজে-কলমে জনপ্রতিনিধিদের অনুমোদনও দরকার ছিল। সে ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরের কর্মচারী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কমিশন আটকানো কঠিন ছিল। এই সমস্যার অবসানের জন্য রাজ্য সরাসরি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। সে ক্ষেত্রে ‘কমিশন না পেলে কাজ হবে না’, এই মানসিকতা দেখানোর সুযোগ কতটা থাকে? তা সত্ত্বেও এই কমিশন আটকানো যাচ্ছে না, তার কারণ উপভোক্তা নির্বাচনের প্রক্রিয়াতে গলদ থেকেই গিয়েছে। শুরুতেই যোগ্য উপভোক্তা বাদ পড়ে যাচ্ছেন, কমিশন না দিতে পারার জন্য। আর কিছু অযোগ্য উপভোক্তার সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাঁরা সরকারি অনুদান অসাধু কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রেও কি এই ভাবে উন্নয়নের জন্য কমিশন প্রথাকে সমর্থন করছেন প্রবন্ধকার?
বনিয়াদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি, যার মাধ্যমে নাগরিকের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবেশের সুরক্ষা প্রভৃতি। শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে খাদ্য দফতরের ধান কেনার ক্ষেত্রে দুর্নীতিও কি, প্রবন্ধকারের কথামতো, উন্নয়নের ‘কমিশন’ আদায়ের প্রক্রিয়া? এর উত্তর জানা দরকার।
দীপ্তার্ক, নোনাচন্দনপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা
গণমুক্তির গান
বিশ্বজিৎ রায়ের “রেখেছ ‘বাঙালি’ করে...” (১৮-১১) প্রবন্ধের সঙ্গে সহমত। বর্তমানে যুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্রের মূল উদ্দেশ্য হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকেই উস্কে তোলা। বিশ্বের দু’প্রান্তে দু’টি যুদ্ধের বীভৎসতা আমরা দেখছি। আরও দেখেছি, শান্তি প্রস্তাবের পক্ষেও ভারতের নিরপেক্ষ ভূমিকা। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঙ্গলার কথা। সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল জোয়ার চলছিল। আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ পুলিশ বহু তরুণ যুবককে গ্রেফতার করছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেফতার হলে বাসন্তী দেবী পত্রিকার ভার নেন, এবং পত্রিকায় একটি কবিতা পাঠানোর জন্য নজরুলের কাছে পাঠান সুকুমার রঞ্জন দাসকে। নজরুল কবিতা লিখে দেন। হুগলিতে জেলবন্দি চিত্তরঞ্জন দাশ ও অন্য বন্দিরা গানটি গাইতেন বলে কথিত আছে। এটি ‘ভাঙার গান’ শিরোনামে বাঙ্গলার কথা (২০ জানুয়ারি, ১৯২২)-য় প্রকাশিত হয়।
গানটি বাংলার মানুষের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে গণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামী ঐতিহ্যবাহী। ফলে গানটির মূল সুরের বিকৃতি বাংলার মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও মানসিকতার আবেগকে আহত করেছে, এবং সঙ্গত কারণেই সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে। তার বাইরেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব ধ্বংসের অন্ধকার সময়ে যা সোনালি আশার আলো।
স্বপন মুনশি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান