ধ্বংসের মধ্যেও কত রকমের সৃষ্টিশীলতা
কলকাতার এই যে নতুন ইতিহাস বইটি হাতে পেলাম, আশা করি এর থেকে আমাদের শহরের আরও অনেক ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি গবেষণার অনুপ্রেরণা মিলবে। গ্রামীণ ও নাগরিক দুনিয়ার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর নির্ভর করে কলকাতা শহরের জীবনযাপন, তার ইতিহাস, তার সংস্কৃতি, তার দারিদ্র, তার উন্নয়ন, তার নাগরিক পরিকল্পনা, তার পরিকাঠামো— এ সবই আস্তে আস্তে ইতিহাস চর্চার মধ্যে ঢুকে আসবে।
সুগত বসু
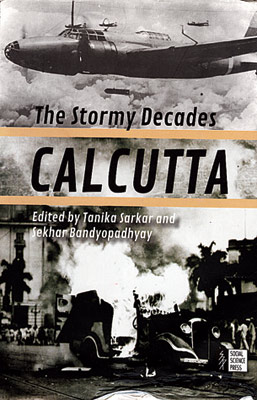
দ্য স্টর্মি ডেকেডস/ ক্যালকাটা, সম্পা: তনিকা সরকার ও শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল সায়েন্স প্রেস/ ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ৮২৫.০০
পনেরো অগস্ট (১৯৪৭) দিনটি যখন স্বাধীনতার জন্য ধার্য হয়ে গেল, গাঁধী ঠিক করেছিলেন, নোয়াখালিতেই সে দিনটি কাটাবেন। ১১ অগস্ট বাংলায় পৌঁছে কিন্তু নোয়াখালি যাওয়ার পরিকল্পনা থেকে তিনি সরে এলেন, কলকাতা নামে ভারতের ‘প্রধান শহর’টিকে যে কোনও ভাবে ‘স্বাভাবিক’ করে তোলাটাই তাঁর কাছে জরুরি মনে হল। ১৩ তারিখ কলকাতার বেলেঘাটায় একটি বাড়িতে এসে উঠলেন তিনি, সঙ্গে রইলেন সোহরাওয়ার্দি। মুসলিম লিগের এই নেতাটিকে যাঁরা অবিশ্বাস করতেন, গাঁধী তাঁদের জানালেন, সেই ফরিদপুর কনফারেন্স থেকে সোহরাওয়ার্দিকে চেনেন তিনি, যে কনফারেন্সে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দিল্লির সব উৎসব উদ্যাপনের থেকে দূরে, অনশন আর প্রার্থনায় তিনি স্বাধীনতার দিনটি কাটালেন। তাঁকে ঘিরে থাকলেন দরিদ্র, অখ্যাত মানুষজন। ভারতের তৎকালীন তথ্য-সম্প্রচার বিভাগ থেকে গাঁধীর বার্তা চাওয়া হল। ‘জাতির পিতা’ একটিই কথা বলতে পারলেন: তাঁর কিছু বলার নেই।
শান্তি আর সহযোগিতার মধ্যেই কাটল কলকাতার ১৫ অগস্ট। পরের দিন, ১৬ অগস্ট, ছেচল্লিশের কালান্তক দাঙ্গার প্রথম বর্ষপূর্তিতে একটি সম্পাদকীয় লিখলেন গাঁধী: ‘মির্যাকল, অর অ্যাক্সিডেন্ট’। লিখলেন, স্বাধীনতার দিন ভোরবেলা কেমন মসজিদের সামনে হিন্দুদের, আর মন্দিরের সামনে মুসলিমদের ‘জয় হিন্দ’ স্লোগান দিতে দেখা গেল, কী ভাবে মিলে গেল তাদের উচ্চারণ। মির্যাকলও নয়, অ্যাক্সিডেন্টও নয়, ঈশ্বরের সুরে সাধারণ মানুষ যখন তার নিজের সুরটি মেলাতে চায়, তখনই এই একত্রতা ঘটতে পারে। ‘আমরা তো পরস্পরকে ঘৃণা করার বিষ-ওষুধটি খেয়ে ফেলেছি, তাই ভ্রাতৃত্বের অমৃত যেন সে দিন আরও মধুর লাগল। সেই মাধুর্যের স্বাদ যেন মেলাবার নয়।’
সে বছরের ইদ ছিল ১৮ অগস্ট। র্যাডক্লিফের সীমান্ত ঘোষণার পর পঞ্জাব জুড়ে তখন নৈরাজ্য, অশান্তি। এ দিকে কলকাতায় কিন্তু সে দিন হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ‘ইদ মুবারক’ বিনিময় চলছে। ২১ অগস্ট গাঁধী প্রসন্নমনে জানালেন যে তাঁর প্রার্থনাসভায় ভারত আর পাকিস্তানের পতাকা পাশাপাশি উড়ছে। আড়াই দশক আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গাঁধী ও শওকত আলি তিনটি জাতীয় স্লোগান বেছে নিয়েছিলেন: ‘আল্লাহু-আকবর’, ‘বন্দে মাতরম্’, আর ‘হিন্দু-মুসলমান কি জয়’। তার মধ্যে শেষ স্লোগানটি সেই অগস্টে কলকাতায় বসে আবার শুনতে পেলেন গাঁধী। তার কয়েক দিন পর, ২৯ অগস্ট, প্রার্থনা সভায় যখন সম্মিলিত কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম’ গানটি গাওয়া হচ্ছিল, সোহরাওয়ার্দি ও স্টেজের উপর উপবিষ্ট অন্য মুসলিমরা গানটির প্রতি শ্রদ্ধাবশত বাকি দর্শকদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। স্টেজের উপর গাঁধী একাই বসে রইলেন। তিনি মনে করতেন, জাতীয় গানের সময় সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা পাশ্চাত্য প্রথা, ভারতে ওটা না হলেও চলে।
অগস্টের শেষে ও সেপ্টেম্বরের গোড়ায় অবশ্য কলকাতায় একটা ছোট মাপের হিংসাত্মক সংঘর্ষ হল। সেপ্টেম্বরের ১ থেকে ৪ গাঁধী আবার অনশনে বসলেন, বিপথগামী কলকাতাবাসীদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য। ‘গুন্ডা’দের বিরুদ্ধে কি অনশন করে কোনও লাভ আছে? তাঁর কাছে জানতে চাইলেন রাজাগোপালাচারি। গাঁধী উত্তর দিলেন: ‘গুন্ডাদের তো আমরাই তৈরি করি।’ যা হোক, কলকাতায় শান্তি ফিরতে দেরি হল না। ৭ তারিখ গাঁধী দিল্লি হয়ে পঞ্জাবের দিকে চললেন। বাংলাকে তিনি বিদায়বার্তা জানালেন বাংলা ভাষায়: ‘আমার জীবনই আমার বাণী।’

১৯৪০-এর দশক যে কলকাতার ইতিহাসকে কতখানি পাল্টে দিয়েছিল, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তনিকা সরকারের সম্পাদিত সাম্প্রতিক বইটি সে কথা মনে করিয়ে দিল। মনে করাল, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগে জর্জরিত একটি শহর চার দিকের ধ্বংসের মধ্যেও সে দিন সাহিত্যে শিল্পে কী আশ্চর্য সৃষ্টিশীলতার স্পিরিট দেখাতে পেরেছিল। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে যদিও মানের ফারাক বেশ প্রকট, তবে কিছু জরুরি প্রবন্ধ এখানে আমরা পাই, বিশেষত তরুণ ইতিহাসবিদদের লেখা। আমাদের নাগরিক ইতিহাস গবেষণাতেও নতুন মাত্রা যোগ করা এখনও কতটাই সম্ভব, লেখাগুলি সেটা প্রমাণ করে। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় জাপানিরা বোমা বর্ষণ করেছিল। সেই বোমার আঘাতে ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেকটাই। খিদিরপুর ডকে সে সময় মৃতদেহের স্তূপে প্রকাশ্যে পচন ধরতে শুরু করে, এমনই ছিল ঔপনিবেশিক শাসকের মনোযোগ। এই ঘটনার উপর লিখতে গিয়ে জনম মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্দৃষ্টিময় মন্তব্য: শবদেহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটিই বুঝিয়ে দেয়, এই সব দেহে যখন প্রাণ ছিল, তাদের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করা হত। তাঁর লেখাতেই পড়ি, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পর কলকাতায় শবদেহ-সৎকার ভ্যানগুলিতে মৃতদের সঙ্গে মৃতপ্রায়দেরও তুলে নেওয়া হত, মূল শহর থেকে শহরের বাইরের ক্যাম্পগুলিতে তাঁদের সরানোর লক্ষ্যে।
কলকাতার মুসলমানদের বৃত্তান্ত এত দিন পরও দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য ও ইতিহাসে একটি অবহেলিত বিষয়। দেশভাগের ফলে কলকাতার কলোনিগুলিতে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ক্লেশ ও দুর্দশার কথা আমরা যতটা পড়েছি, কিংবা সিনেমায় দেখেছি, কলকাতার মুসলিমদের এই শহর থেকে উৎপাটন কিংবা প্রান্তিকীকরণের কথা মোটেও ততটা জানতে পারিনি, এমনকী তার বিশেষ উল্লেখও পাইনি। অন্বেষা সেনগুপ্তের সুলিখিত প্রবন্ধটি কলকাতার মুসলমানদের সংকটের ছবিটি তুলে ধরল, বিশেষত অধুনা-বিস্মৃত ১৯৫০-এর দাঙ্গার পরবর্তী সময়কালে।
যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর দেশভাগ একাধারে যে শহরকে ধ্বংস করতে বসেছিল, বিভিন্ন দিক থেকে তার অনুসন্ধান এই বইয়ে। তার মধ্যে, ১৯৩০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে কলকাতা শহরের নাগরিক পরিসরটির নতুন নির্মাণের বিষয়ে কতকগুলি ভাল লেখা পেলাম আমরা। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর ওপর পার্থ দত্তের লেখায় পড়লাম অমল হোমকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি: ‘আমাদের দেশ স্বাবলম্বী হচ্ছে। আমাদের শহরগুলিকেও ক্রমে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পবোধ নিজেদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমি অপেক্ষা করে থাকব, কবে কলকাতায় এই বোধ প্রতিফলিত হতে শুরু করে।’
আজকাল যখনই যাদবপুরের নির্বাচনী এলাকায় যাই, মনে পড়ে, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সত্যজিৎ রায় আমাদের শহরের খুব কাছে বোড়াল অঞ্চলটিকে বেছে নিয়েছিলেন ‘পথের পাঁচালি’র শুটিং-এর জন্য। আজ বোড়াল বেশ ঘন জনবহুল, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার অন্তর্গত একটি শহুরে এলাকা। দক্ষিণ কলকাতার যে সব শহরতলিতে সাতচল্লিশের দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা বসবাস শুরু করেছিলেন, সেই সব অঞ্চলের সঙ্গে আজ আর তার কোনও ফারাক চোখে পড়ে না। নাগরিক কলকাতা এ ভাবেই প্রসারিত হচ্ছে, বোড়াল থেকেই আরও দক্ষিণে বারুইপুর অবধি চলে গিয়েছে তার আওতা। বারুইপুর পেরোনোর পর তবেই আস্তে আস্তে চোখে পড়বে মাঠঘাট, ফলের বাগান— মূল মহানগরে ফলমূল-শাকসব্জির রফতানি চলে যে সব জমি-জায়গা থেকে।
কলকাতার এই যে নতুন ইতিহাস বইটি হাতে পেলাম, আশা করি এর থেকে আমাদের শহরের আরও অনেক ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি গবেষণার অনুপ্রেরণা মিলবে। গ্রামীণ ও নাগরিক দুনিয়ার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর নির্ভর করে কলকাতা শহরের জীবনযাপন, তার ইতিহাস, তার সংস্কৃতি, তার দারিদ্র, তার উন্নয়ন, তার নাগরিক পরিকল্পনা, তার পরিকাঠামো— এ সবই আস্তে আস্তে ইতিহাস চর্চার মধ্যে ঢুকে আসবে।



