

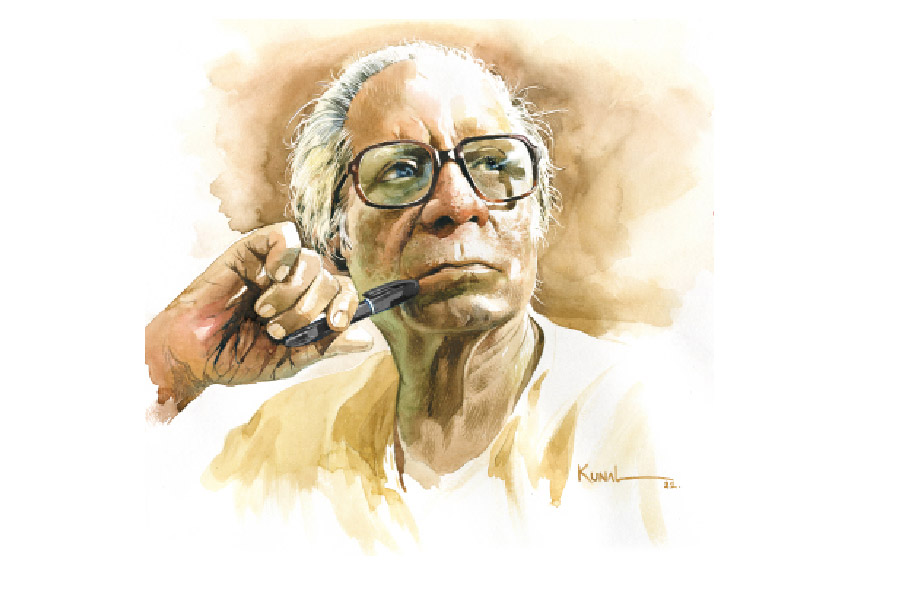
ছবি: কুনাল বর্মণ।
সাংঘাতিক লোক!
ভাড়াবাড়ির এক চিলতে নিভৃত ঘর। রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত আলো জ্বলে। এক চিলতে টেবিলে লিখে চলেছেন মানুষটা। কিন্তু সে জন্য নববধূটি দু’চোখের পাতা এক করতে পারেন না। বিয়ের আগে শুনেছিলেন বটে, বরটি সাহিত্যিক। তা সাহিত্য রচনা করুন। কিন্তু আলো? কথাটা পাড়তেই উত্তর, “ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।” পরের দিনই টেবিল ল্যাম্প নিয়ে হাজির যুবক সাহিত্যিকটি। স্ত্রীর চোখে যাতে আলো না লাগে, সে জন্য লন্ঠনের চার পাশ কাগজ দিয়ে আড়াল করলেন।
যাক, বিয়ের আগে যে কথাটা ভেবেছিলেন, সেটা মিলল না। স্মৃতির খাতা খুলে কথাটি উপহার দেন সুষমা চৌধুরী, সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর স্ত্রী। সুষমার বাপেরবাড়ি বর্ধমান শহরে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে। সুষমা শুনেছেন, সম্বন্ধ হয়েছে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় চাকরি করেন, এমন একটি ছেলের সঙ্গে। এক প্রস্ত দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। এ বার ছেলেটি আসবে। সুষমা ভয়ে কাঁটা। মাকে বলেন, “মা, আনন্দবাজারে চাকরি করে। ওরা কিন্তু খুব সাংঘাতিক লোক হয়!” মা আশ্বস্ত করেন মেয়েকে, “আহা, তোকে কি খবরের কথা জিজ্ঞাসা করবে?”
যুবক রমাপদ এলেন। কথাবার্তা কিছুই হল না। একটি পান মুখে দিয়ে, আর একটি হাতে নিয়ে ফিরতি পথে বর্ধমানের বাড়ির পাশে, যুবতীটির বাবা, দাদা, পরবর্তী সময়ে ননদাইয়ের সঙ্গে আড্ডায় ডুব দিলেন রমাপদ। আড্ডার মাঝে ছুটে এলেন সুষমার বাবা। বললেন, “ছবি (সুষমার ডাকনাম), জানলাটা ফাঁক করে দেখ। ছেলেটিকে তোর পছন্দ কি না। আমার খুব পছন্দ। গায়ের রংটা চাপা। কিন্তু মুখ-চোখ খুব তীক্ষ্ণ। অসাধারণ কথা বলে।” দুধে-আলতায় গায়ের রং, ডাকসাইটে সুন্দরী সুষমা এক চিলতে দেখলেন ছেলেটিকে। একটা যেন টান অনুভব করলেন।
টান অনুভব করলেন রমাপদও। বিয়ের পর রমাপদর সঙ্গে সুষমা উঠলেন কলকাতার অমৃত ব্যানার্জি রোডের ভাড়াবাড়িতে। পরে আরও একটি ভাড়াবাড়ি, গল্ফ গ্রিনের একতলার নিজস্ব ফ্ল্যাট ঘুরে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের উপরে ফ্ল্যাট, এই হল রমাপদ-সুষমার সংসারের ভৌগোলিক অবস্থান। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে সুষমা দেখলেন, প্রায় তিরিশ জন লোক! সবই যেন গুলিয়ে যায়। তার উপরে রয়েছেন এক বয়ঃজ্যেষ্ঠা। তিনি কড়া নজরে রাখেন নববধূকে। চলে ঘোর আড়ি পাতা।
কিন্তু এ সবকে বুড়ো আঙুল, স্ত্রীকে ক্ষণে-ক্ষণে চমকে দেন ‘সাংঘাতিক লোক’টি। এক দিন রমাপদ জানলেন, সুষমা একটা বই পড়ছিলেন। কিন্তু কেউ তা সরিয়ে ফেলেছেন। মাঝপথে ছিল যে গল্পটা! দ্রুত সুষমার জন্য হাজির নতুন বই।
আবার এক দিন দ্রুত কাজ সেরে বাড়ি ফিরলেন রমাপদ! স্ত্রীকে বললেন, “খাবার বলা আছে। বেরোব। তৈরি হও।” বুঝতে পারেন না সুষমা, কোথায় যাওয়া। খানিক বাদে দেখা গেল, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নাইট-শোতে সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন রমাপদ। এ ভাবেই গিয়েছেন লেকের ধারে; তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্রের নাটক, উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখতে। যান রবীন্দ্রসদনেও। সেখানেই এক দিন। ‘একা এসেছো?’ রমাপদকে জিজ্ঞাসা এক জনের। ‘না, স্ত্রী’ও আছে।’ ‘কই ডাকো, তাঁকে তো দেখিনি আগে’। সুষমা প্রণাম করলেন মানুষটিকে। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ, ‘চিরসুখী হও।’ আশীর্বাদটি করলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।
কিন্তু ‘চিরসুখী’ সুষমার কাছে ‘ধরা’ পড়েছেন খোদ রমাপদই। রমাপদ বাজার করেন সপ্তাহে এক দিন, রবিবার। সুষমা দেখেন, প্রতি বারই বাজার থেকে ফিরে বাজারের থলি হাতে ধরিয়ে রমাপদ বলেন, “এই নাও। হাজার টাকার বাজার।” কিন্তু সুষমার হিসাব মেলে না। এক হাজার টাকায় এত অল্প বাজার! হঠাৎ খেয়াল হল, রমাপদ বাজারের থলিটি হাতে ধরিয়েই কাগজে মোড়া কিছু একটা নিয়ে লেখার টেবিলের পাশের আলমারিতে তুলে রাখেন। এক দিন তাতেই নজর সুষমার। বেরিয়ে এল এক কার্টন সিগারেট! সিগারেট সারা জীবনে বার তিনেক ছেড়ে, বার তিনেক ধরেছেন রমাপদ।
সিগারেট যে বিষ, তা পইপই করে স্বামীকে বলেছেন সুষমা, হয়তো বা অজানা কিছুর আশঙ্কা থেকে। যদিও, মৃত্যুর পরেও রমাপদ আর তাঁর স্মৃতিরা ঘোরাফেরা করে সুষমার অন্দরমহল, বাহিরমহলে। রমাপদ স্ত্রীকে বলে গিয়েছেন, “আমি চলে যাওয়ার পরেও তুমি যেমন আছো, তেমনই থেকো। আমি পছন্দ করি না ও-সব।” রমাপদর ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে সুষমাও ‘বৈধব্য’ কথাটিকে অস্বীকার করেছেন।
এই দম্পতির দুই কন্যা, মহুয়া ও মঞ্জরী। বড় মেয়ে মহুয়ার পারিবারিক স্মৃতিতে বাবা রমাপদর বাৎসল্য-পরিচয়। মহুয়া তখন বেশ ছোট। অষ্টমীর সন্ধ্যা। বাবা ফিরলেই ঠাকুর দেখতে যাওয়া হবে। রমাপদ অফিস থেকে ফিরেছেন। ছুটে সে সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে একরত্তি মহুয়া পড়লেন গরম দুধে। প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কার্যত এক মাস বিনিদ্র রাত কেটেছে রমাপদর। ঠিক তার পরের পুজোয়, অষ্টমীতেই ওই মেয়ে ভীষণ জ্বরে পড়ল। এর পরে পুজো এলেই রমাপদ ভয়ে থাকতেন, না জানি এ বার কী হয়। অথচ, এই রমাপদ বড়ই কালীভক্ত। লেখা শেষ করে দপ্তরে পাঠিয়েই কালীঘাট মন্দিরের বাইরে থেকে মাতৃমুখ দর্শন করা চাই-ই। করতেন কোষ্ঠী-বিচারও। পরে অবশ্য জ্যোতিষেও বিশ্বাস উঠে যায়।
পরীক্ষাগারে মধ্যবিত্ত
বস্তুত, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংশয়-দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশা, শান্তি-অশান্তিতে সাজানো মধ্যবিত্তের ঘর। এই ঘরটি তৈরি হয় বিত্ত, বিদ্যা, পেশা, রুচি, এই চারটি নির্মাণ-সামগ্রী দিয়ে। বঙ্গদেশে এর উদ্ভব ইংরেজ শাসনের শুরুর দিকে। উনিশ শতকে এর বিস্তার। কিন্তু বর্তমানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, মধ্যবিত্ত নিছক এক জনগোষ্ঠী নয়। বরং এক ‘মানসিকতা’। সমাজবিদ বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভাঙার পরে, ধনতন্ত্রের বিস্তারের সময়, এই মানসিকতা কী ভাবে সংক্রমিত হয়েছে নানা বিত্ত, রুচি, শিক্ষার মানুষের মধ্যে। কালক্রমে সে মানসিকতায় বদলের দোলা লেগেছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতার ধারক আদতে তাঁরা, “বংশানুক্রমে যারা একটি বিশাল নাগরদোলায় বসে আছে। কখনো ওপরে উঠছে কখনো নীচে নামছে, কিন্তু বৃত্তের বাইরে কদাপি নয়।”— রমাপদর সাহিত্যের পরীক্ষাগারে ধরা পড়ে মধ্যবিত্ত-ঘরের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের এই বৃত্তটিই।
আর তাই, ‘প্রথম প্রহর’, ‘দ্বীপের নাম টিয়ারঙ’, ‘অরণ্য আদিম’ প্রভৃতি লিখলেও মনের তৃপ্তি পান না রমাপদ। চরিত্রগুলিকে তিনি দেখেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজে এদের প্রতিনিধি নন। তিনি প্রতিনিধি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। এই সূত্রেই আসে ‘খারিজ’। বালক-পরিচারক পালানের মৃত্যু ঘটে। কথক চরিত্র, চাকরিজীবী জয়দীপের মধ্যে মধ্যবিত্তের স্ববিরোধী অবস্থানটির খোলস ছাড়ালেন রমাপদ। তাই, পালানকে শীতের রাতে খোলা বারান্দায় শতরঞ্জির মতো পাতলা তোশক আর ছেঁড়া চাদর দেওয়াটা জয়দীপদের অপরাধ নয়। কিন্তু অভিজিৎ নামে চরিত্রটি যখন বেয়ারাকে গিয়ে জুতো খোলায়, তখন জয়দীপদের মনে হয়, মানুষের আত্মমর্যাদা মাটিতে মিশে গেল।
আসলে মধ্যবিত্তের লজ্জা আছে ও মধ্যবিত্ত চায়, তা থাকুক গোপনে। ‘লজ্জা’ আর ‘চড়াই’ এই গোপন কথাটিই। ‘চড়াই’-তে নিরূপার সহোদর অভি আর স্বামী অবনী চায় মধ্যবিত্ত মানসিকতার উপরের ‘স্টেটাসে’ যেতে। নানা ঘটনাপ্রবাহে ‘চড়াই’ নিরূপাকে কেন্দ্র করে হয়ে ওঠে মধ্যবিত্ত মেয়ের দাম্পত্য-সঙ্কট, তা থেকে বেরিয়ে আসার সাহস অর্জনের আখ্যান। নিরূপা আত্মহত্যার চেষ্টাও করে এক সময়। কিন্তু তা ‘গোপন’ রাখতে হবে, এই ছিল তার বাপের বাড়ির অভিপ্রায়। নিরূপার বাবা আনন্দমোহনের মুখে রমাপদর বলা কথা, ‘কেবল গোপন করো, লুকিয়ে রাখো।’
গোপন-কথা যে সময়বিশেষে আঘাতও দেয়, তা আমরা বুঝেও বুঝি না। তাই ‘লজ্জা’য় কিছু সমস্যা থাকা রেণুকে আঘাত করাটাই যেন স্বাভাবিক! এমন স্বাভাবিক ভাবেই মধ্যবিত্ত পরিবার শিক্ষিত, কিন্তু আর্থিক ভাবে অসচ্ছল মানুষটিকে কী ভাবে দূরে সরিয়ে দেয়, তার প্রমাণ ‘হৃদয়’-এর শুভেন্দু। শুভেন্দুদের কাছে ভালবাসা, বিয়ের কথা ভাবাটাই অপরাধ। তাই তার মনে হয়, “ভালবাসা পরমার্থ হতে পারে, কিন্তু তাকেও টাকার পায়ে দাঁড়াতে হয়।” টাকার গুরুত্ব বোঝে বলেই, শুভেন্দু দেখতে পায় ভাই নবেন্দু, তার পরিবার ‘...কতবদলে যাচ্ছে।’
বস্তুত মধ্যবিত্ত বদলায় দ্রুত, আর তার মধ্যে চলে এক নিয়ত আত্ম-আবিষ্কার। ‘বীজ’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, পেশায় অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর, এই স্ব-আবিষ্কার এবং নিঃসঙ্গতার প্রতিনিধি। আটচল্লিশ বছর বয়সে এসে সে বৃষ্টির সৌন্দর্য টের পায়। কিন্তু দেখে, তত দিনে বাড়ির কারও আর তার সঙ্গে কথা বলার অবকাশ নেই। সে পালিয়ে যায়। কিন্তু তখনই তার স্ত্রী সুধাময়ীর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, শশাঙ্কশেখরের কাগজের টুকরোয় লিখে রাখা অপর্ণার নাম। আবার নিজের আত্মসম্মানের কথা ভেবে চায়, ফিরুক শশাঙ্কশেখর। বস্তুত, সাহিত্যিকের নিজের ভাষায় এ এক ‘দামী মানুষদের মূল্যহ্রাসের গল্প’!
মধ্যবিত্তের কাছে মানুষের মূল্য আদতে মনস্তত্ত্বের নিক্তিতে মাপা। প্রমাণ, ‘বাহিরি’। নুলো ভিখিরির হাতুয়া পরিচিতি পায় বংশীধর হিসেবে, মধ্যবিত্ত সুধাময়ের মহানুভবতায়। কিন্তু এই বংশী যখন জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সমান-সমান হতে চায়, হয়তো বা ছাড়িয়েও যেতে চায় তাকে, সুধাময়ের কাছে ‘তখন সে অসহ্য, অসহ্য’!— আদতে মধ্যবিত্তের সহ্য-অসহ্যের ধারণাটা আপেক্ষিক। তাই ‘বাড়ি বদলে যায়’-তে পড়শি ভাড়াটের উচ্ছেদ দেখে যে ধ্রুব ছিল সহানুভূতিশীল, সেই ধ্রুবই বাড়ির মালিক হয়ে বলে, “শালা ভাড়াটেদের জ্বালায় টেকা দায়।” দেখেশুনে স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, “...বাড়িটা সত্যি বদলে গেছে।”
এমন বদল বা দ্বৈত সত্তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে ‘রূপ’ উপন্যাসটি। মা ও বোনের সঙ্গে ‘ছলনা’ করে নিখিলেশ স্ত্রী করবীকে নিয়ে পুরীতে চলল। কিন্তু গত দু’বছর স্ত্রীকে যেমন দেখেছে, পুরীতে এসে সে যেন এক দম আলাদা। বান্ধবীর স্বামীর কথার উদাহরণ টেনে সে বলে, “অঞ্জলির স্বামী, জানো, খুব বড় অফিসার।” আবার কল্যাণসুন্দর চরিত্রটিকে সামনে এনে এক ছাদের তলায় থাকা নারী-পুরুষের সম্পর্কের ফাঁকফোকরগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। তাই যে নিখিলেশ ভিতু, লাজুক মেয়েটির ‘ঘুমন্ত শিল্পীমন’-কে চিনেছিল, এখন সেই নিখিলেশই স্ত্রীর মধ্যে দেখছে ‘একটা নির্মম নৃশংস মানুষ।’ ক্রমে নিখিলেশেরও আত্ম-পরিচিতি সংশয়ে পড়ে। কোনটা সত্যি, কোনটা আসল, মধ্যবিত্তের এই ধন্দটি আমাদের দেখান রমাপদ।
মধ্যবিত্তকে রমাপদ ফালাফালা করেছেন তাঁর ছোটগল্প ‘জাল’, ‘আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া’, ‘দিনকাল’, ‘ফ্রীজ’ প্রভৃতিতে। পাশাপাশি, রমাপদর অর্থনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও সুগভীর। তাই ‘ভারতবর্ষ’-এ যুদ্ধের সময়ে পালামৌয়ের এক গ্রামের ‘ভিখিরি’ হয়ে ওঠা, ‘বনপলাশীর পদাবলী’ উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশে গ্রামের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড চুরমার হয়ে যাওয়া দেখাতে পারেন অক্লেশে। অন্য দিকে, একই সাবলীলতায় ছুঁতে পারেন ঐতিহাসিক কালকে, ‘লালবাঈ’-এর মাধ্যমে।
এ সব আখ্যান সিনে-পর্দাকেও টেনেছে বার বার। তাঁর কাহিনি নিয়ে সিনেমা করেছেন মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গুরু বাগচী, এমনকি উত্তমকুমারও। লেখালিখির সূত্রে পুরস্কারের তালিকাও হয়েছে দীর্ঘ: আনন্দ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, অকাদেমি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী পদক’, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট-সহ আরও কত কী। অথচ, এই মানুষটিকেই ‘পত্রনবীশ’ ছদ্মনামে ফিচার লিখে, টাকা জমিয়ে প্রকাশ করতে হয় প্রথম তিনটি গল্পগ্রন্থ। তাঁর আর একটি ছদ্মনাম, ‘অর্জুন রায়’। পাশাপাশি, রমাপদর ক্ষুরধার গদ্য ও পুস্তক-সমালোচনাগুলিও অত্যন্ত জরুরি। যেমন, গুন্টার গ্রাসের কলকাতা সংক্রান্ত একটি বইয়ের অনুবাদের সমালোচনায় তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, “বেশ বোঝা যায় ‘দি ঈস্ট ইজ ঈস্ট, দি ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, দ্য টোয়েন শ্যাল নেভার মিট’-এর যুগ থেকে গ্রাস একটুও এগোননি।”
এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে সাহিত্যিকের অধিকার, তিনিই আবার সাহিত্য জগৎ থেকে ‘অবসর’ নিয়েছেন প্রায় ঘোষণা করেই!
জহুরির নজর
শুধুই সাহিত্যিক নন, বাফতা-র গেরুয়া বা অন্য রঙের রঙিন পাঞ্জাবি, সাদা ধুতি, কোলাপুরি চটিতে শোভিত রমাপদ আনন্দবাজার পত্রিকার কিংবদন্তি সাংবাদিক ও সম্পাদকদের এক জনও। অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর হিসেবে দীর্ঘ দিন সম্পাদনা করেছেন ‘রবিবাসরীয়’ বিভাগটি এবং আনন্দবাজার পত্রিকার পুজো সংখ্যা। সম্পাদকের রাশভারী মেজাজের পরিচয় পেয়েছেন অনেকেই। তেমনই এক জন সমরেশ মজুমদার। ১৯৬৭ থেকে ‘দেশ’-সংযোগ সমরেশের।
দৃশ্যটা এরকম: চোখ বন্ধ করে অফিস-ঘরে ভাবছেন রমাপদ। ঢুকলেন সমরেশ। বললেন, “দেশ-এ লিখি। একটা গল্প নিয়ে এসেছি।” চোখ বন্ধ করেই রমাপদর জবাব, “গল্পটা দেশ পত্রিকাতেই নিয়ে চলে যান!” দূরত্ব তৈরি হল দু’জনের। ঘুচলও। ১৯৭৮-এর এক দিন। আনন্দবাজারের অফিসে ঢুকছেন সমরেশ। মুখেই দেখা রমাপদের সঙ্গে। বললেন, “একটা লেখা দেবেন তো!”এটুকু বলেই চলে গেলেন। পরে, ঘনিষ্ঠতা বাড়লে সমরেশকে দেখলেই আহ্বানও জানিয়ে রেখেছেন, “বিকেলে মুড়ি খেয়ে যাবে!”
রমাপদর এমন অদ্ভুত আচরণের সাক্ষী প্রয়াত দিব্যেন্দু পালিতও। মৃত্যুর মাস পাঁচেক আগে সে কথা শুনিয়ে যান দিব্যেন্দু। পুজো সংখ্যার জন্য গল্প চেয়েছেন রমাপদ। তা দিতে খুবই দেরি হল দিব্যেন্দুর। যখন দিলেন, রমাপদ বললেন, “এত দেরিতে দিলে কি ছাপা সম্ভব? ছাপার কাজ তো শুরু হয়ে গিয়েছে... দেখছি কী করা যায়...।” কয়েক দিন পরে বিজ্ঞাপন বেরোল পুজো সংখ্যার। লেখক তালিকায় দিব্যেন্দুর নাম নেই। হতাশ বেশ। এমন সময় রমাপদর জিজ্ঞাসা, “কেমন লিখেছেন গল্পটা?” দিব্যেন্দু: “চেষ্টা করেছি এই মাত্র।” রমাপদ: “শুধু চেষ্টা করেছেন, না আরও কিছু?” দিব্যেন্দুর বিনীত জবাব, “না, চেষ্টাই তো...” এর পরেই সম্পাদক রমাপদের রূপটি দেখা গেল। চা খাইয়ে তরুণ দিব্যেন্দুকে বললেন, “এরকম গল্প যদি আপনি আরও দু’টি লেখেন, তা হলে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিতে পারবেন।” পুজো সংখ্যায় বেরোলে, দিব্যেন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেই গল্প, ‘মাড়িয়ে যাওয়া’। এ ভাবেই বহু তরুণ লেখককে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছেন রমাপদ।
সম্পাদনার কাজে রমাপদর এক ধরনের ‘আশ্চর্য দক্ষতা’ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও। লেখা চেনা, কাকে দিয়ে কী লেখানো সম্ভব, কোনটা চয়ন করা হবে, এ সব বিষয়ে রমাপদর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু এখানেও মধ্যবিত্তের বিশ্বাস, মূল্যবোধকে বিসর্জন দেন না রমাপদ। তাঁর নিবিড়তম বন্ধুদের এক জন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি আনন্দবাজারে যোগ দেন ১৯৫১-র ২ ডিসেম্বর। তার কিছু দিন পরই যোগ দেন রমাপদ। তরুণ লেখকদের রাশভারী রমাপদর কাছে পৌঁছনোর অন্যতম মাধ্যম মিশুকে নীরেন্দ্রনাথ। এ হেন নীরেন্দ্রনাথকে সঙ্গী করেই রমাপদ অফিস থেকে বেরিয়ে কোনও দিন যান চাচা-র শিক কাবাব, কোনও দিন দিলখুশার মাটন কাটলেট খেতে— গল্পটা শুনিয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ-পুত্র কৃষ্ণরূপ। এ সবের পাশাপাশি, ফল্গুধারার মতো দু’জনের মধ্যে থাকে গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তাই, নীরেন্দ্রনাথ যখন কোনও তরুণ লেখকের লেখা এনে বলেন, “রমাপদ একটু পড়ে দেখ তো।” চোখ বন্ধ করে তা ছাপাখানায় পাঠান রমাপদ।
নীরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, সন্তোষকুমার ঘোষের কন্যা কাকলিদেবীরও স্মৃতিতে আছে শ্বশুরমশাইয়ের বলা কথাগুলি। বলেছিলেন, নীরেন্দ্রনাথের মতো ‘প্রোডাকশন’ বোঝার লোক কলকাতা শহরে আর এক জনও যদি থাকে, তবে তিনি রমাপদ। কাকলিকে রমাপদ শিখিয়েছেন সম্পাদনার নানা খুঁটিনাটি। আর বিশিষ্ট পত্রিকা-সাংবাদিক কাকলি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন, রমাপদর ‘বিরল হাসি’!
এ হেন বন্ধু-বিয়োগে (২৯ জুলাই, ২০১৮) স্বাভাবিক ভাবে খুবই ভেঙে পড়লেন নীরেন্দ্রনাথ। রমাপদর স্ত্রী সুষমাকে নীরেন্দ্রনাথ রুদ্ধ-কণ্ঠে আশ্বস্ত করলেন, “তুমি চিন্তা কোরো না, আমারও আর দেরি নেই। রমাপদকে বেশিদিন একা থাকতে হবে না।... ও খুব শিগগিরই কথা বলার লোক পেয়ে যাবে।” সত্যিই মাত্র কয়েকটা মাস অপেক্ষা। নীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু ওই বছরই, ২৫ ডিসেম্বর!
‘বাবার মতো’ হতে
রমাপদকে ঘিরে এই যে এত লেখা-পড়া, কাগজ-কলমের সংসার, এর শুরুটা হয় ১৯৪০-এ। ওয়াইএমসিএ রেস্তরাঁয়, বন্ধুদের পাল্লায় ও কার্যত পাহারায় রমাপদ লিখলেন প্রথম গল্প ‘ট্র্যাজেডি’। কিন্তু রমাপদ বোধহয় সাহিত্যিক হওয়ার কথা ভাবেননি। বরং, কী হবেন, তা ধারণা ছিল না। অনেকের মতো তিনিও হয়তো ভেবেছিলেন ‘বাবার মতো’ হবেন। তবে সে সব ভাবনার বাইরে গিয়ে, ছোট থেকেই দু’চোখ ভরে দেখেছেন, মানুষ। দেখার শুরুটা (জন্ম ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২), বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রধান শহর, ‘মিশ্র সংস্কৃতি’র খড়্গপুরে ‘সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান’ নম্বরের বাংলোটি থেকে। বাবা তারাপ্রসন্ন চৌধুরী। মা হরিদাসী।
রমাপদ এই শহরেই দেখেছেন বিলিতি ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব, হাতে গোনা বাঙালি, দক্ষিণ ও মধ্যভারত, পূর্ববঙ্গের লোকজনের নানা রূপ। তাঁদের বাসস্থান ও মানসিকতার বিভিন্ন খোপগুলি। বস্তুত এই খোপগুলি নির্ধারিত হয়েছে পেশার মান ও স্থান অনুযায়ী। কিশোর রমাপদর যেন সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়, যখন দেখেন অন্য শ্রেণির মানুষের বিষ্ঠা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক দল মানুষ। অথচ, ওরা মেথর, ওদের এটাই কাজ, এমন একটা ভাবনা থেকে মধ্যবিত্ত মানুষ কী স্বাভাবিক ভাবে এই দৃশ্যটিকে গ্রহণ করেছে।
বস্তুত, মধ্যবিত্ত মানসিকতা কী ধরনের বিষ ছড়িয়েছে সমাজে, তা রমাপদ টের পেলেন ওই কৈশোরেই, বয়ঃসন্ধির কালে। পড়শিদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছেন। কংসাবতীতে ডুব দিয়ে উঠে আসা পড়শি লীলাবৌদিকে দেখে সাহিত্যে পড়া ‘সিক্তবসন’ শব্দটির তাৎপর্য যেন বুঝতে শেখেন। সেই লীলাবৌদির সোনার হার হারিয়ে গেলে, তা খুঁজে দেন রমাপদ। বদলে, এক হাঁড়ি রসগোল্লা খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন লীলাবৌদি। কিন্তু তাঁর বাড়ির কাছে গিয়ে রমাপদ আড়াল থেকে শোনেন লীলাবৌদির স্বামীর কথা, “আরে বাবা, ছেলেটা নিজেই হারটা লুকিয়ে রেখেছিল, বেকায়দায় পড়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।”
তবু এই শহরই যে রমাপদর প্রথম সব কিছু। চিনতে শেখা রেলকে কেন্দ্র করে তৈরি সাম্যের পরিবেশ। দেখেন, রেলের হাসপাতালের কাছেই দুই কম্পাউন্ডার এক জন ব্রাহ্মণ, অন্য জন মেথরের পাশাপাশি কোয়ার্টার। চিনতে পারেন নিজের মাকে, আমাদের বাড়ির নিভৃতে থাকা মায়েদেরও। তাঁরা যে গর্ব করার মতো মানুষ, এ-ও বোঝেন। ঘটনাটা পুজোর সময়ের। প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে। সেখানে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারও উপস্থিত। তিন জন তড়িদাহত আচমকা। সবাই হতচকিত। মা মন্দিরের ভিতর থেকে ছুটে এসে প্লাগ আর তার আলাদা করে প্রাণ বাঁচালেন তিনটি মানুষের।
রমাপদর মা আটপৌরে, কিন্তু বাবা তারাপ্রসন্ন শৌখিন, বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, গণিত ও সংস্কৃতেও বিশেষ পারদর্শী। পৌঁছেছেন রেলের অ্যাকাউন্টস বিভাগের সর্বোচ্চ পদে। ভালবাসেন বাঁশি বাজাতেও। এমন রঙিন কিন্তু গম্ভীর মানুষটি শ্রমিক সংগঠনও করেন। সে সূত্রে ঘনিষ্ঠতা ভি ভি গিরির সঙ্গে। যাঁকে নিয়ে পরে রমাপদর উপন্যাস ‘ছাদ’।
বাবার কাছে পড়েই ম্যাট্রিকুলেশনে অঙ্ক আর সংস্কৃতে লেটার নম্বর রমাপদর। বাবা জানতে চাইলেন, কী নিয়ে পড়বে। অত্যন্ত ভাল ফল করা রমাপদর উত্তর ‘আর্টস’। শুরু হল নতুন জীবন— প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু হস্টেল, কলেজ স্ট্রিট আর মহানগর কলকাতাকে সঙ্গী করে। আর ঠাঁই হল বেকার ল্যাবরেটরির উল্টো দিকে ইডেন হিন্দু হস্টেলে, ওয়ার্ড নম্বর চার, পূর্ব দিকের তিনতলা অংশটির দোতলায়। কলেজের সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র রমাপদর পরিচয় নতুন শব্দের সঙ্গে, ‘BURSAR’। বারসার মানে ক্যাশিয়র বা হিসাবরক্ষক।
কলেজের অন্দরমহলে তখন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারকনাথ সেন, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, সুশোভন সরকার প্রমুখ দিকপালদের আনাগোনা। কাছাকাছি ক্লাসে রয়েছেন অমলেশ ত্রিপাঠী, অম্লান দত্তের মতো তুখোড় ছাত্ররা।
তারকনাথ সেনের প্রসঙ্গে একটি চমৎকার গল্প শুনিয়েছেন রমাপদ। আন্দ্রে মরোয়ার লেখা লর্ড বায়রনের জীবনী। কলেজের গ্রন্থাগার থেকে নিয়েছেন। বিস্ময়ে দু’রাত জেগে পড়ে ফেলেছেন। এ বার বইটি ফেরত দেবেন। বাসে উঠেছেন, হাতে বইটি রয়েছে। পাশাপাশি বসে তারকবাবু ও রমাপদ। হাতের বইটি দেখে তারকনাথের মন্তব্য, “ইট’স আ নভেল।” সঙ্গে জীবনী পড়তে হলে কী-কী বই পড়া দরকার, তার তালিকাও দিলেন। কিন্তু ‘অ্যাকাডেমিক্সের সঙ্গে সাহিত্যের এই বিরোধ’টা বোধহয় মানতে পারলেন না রমাপদ।
এ সব নানা টুকরো অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করেই রমাপদ কালে-কালে মায়ায় জড়ালেন কলেজ ও হস্টেলের। এক দিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মশগুল। হঠাৎ উপস্থিত বাবা। উদ্দেশ্য, শীত পড়েছে। ছেলেকে আলোয়ান কিনে দিতে হবে। মানি অর্ডার করেননি, চিঠিতে নির্দেশও দেননি। নিজে এসেছেন, এতটা পথ পেরিয়ে, শুধু একটি শাল কিনে দিতে। ছেলেকে কলেজ স্ট্রিটের শাল মিউজ়িয়ম থেকে কিনে দিলেন কাশ্মীরি আলোয়ান। কিন্তু ঘটল এক বিপত্তি। হস্টেলে চুরি হল। বইগুলি ঠিকই আছে। শালটা চুরি গিয়েছে। ধার করে প্রায় সে রকমই একটি শাল কিনলেন রমাপদ। কিন্তু ঘটনাটার কথা বাবাকে কোনও দিন বলা হয়নি রমাপদর। কেন? উত্তরটা নিজেই দিচ্ছেন। “আত্মসম্মান? অথবা আমার ওপর বাবার আস্থা হারানোর ভয়ে?”
তবুও আনন্দ
এই আস্থা হারানো সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষই রমাপদকে সমৃদ্ধ করে চলে। আর তা-ই হয়ে ওঠে সাহিত্য। কখনও খড়্গপুর শহরে দেখা ইরানি মেয়েদের নিয়ে লেখেন ‘কাল আয়ো’। এমন আরও প্রচুর থাকলেও, দু’টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ধমানের পলসোনা গ্রাম, রমাপদর দেশের বাড়ি। পলাশবনার অপভ্রংশ। এটিকেই বদলে ‘বনপলাশী’ নামটি নিলেন তিনি। এই গ্রামেই দেখা কিশোরী রিনার চোখে চিনতে শিখলেন গ্রাম। আর তাই তাঁর স্বীকারোক্তি, ‘বনপলাশির পদাবলী আমাকে কে লিখিয়েছিল? ওই ন’-দশ বছরের কিশোরী মেয়ে রিনা।’ এই রিনাকে নিয়েই লেখা ‘জনৈক নায়িকার মৃত্যু’ গল্পটি।
এ ভাবে গল্পের চরিত্র হয়েছেন ফেলে আসা স্কুলের এক প্রধান শিক্ষকও। রমাপদ তখন যথেষ্ট বিখ্যাত। কলকাতার বাড়িতে অসুস্থ। সে খবর শুনে বৃদ্ধ মাস্টারমশাই প্রায়ই চলে আসেন মেদিনীপুর থেকে, কবিরাজি ওষুধ, তমলুকের বড়ি, পাকা বেল সঙ্গে করে। সঙ্কোচ বোধ করেন রমাপদ। এ ভাবে আসা, এতটা রাস্তা। শুনে মাস্টারমশাই বললেন, ‘আসব না? ...তুমি যে আমার কত বড় গর্ব তুমি বুঝবে না।’ মাস্টারমশাইকে নিয়েই ‘গুরুদণ্ড’।
মধ্যবিত্তের খামতি, তার মধ্যেই এই যে আস্থা না হারানোর প্রত্যয়, তা চেনাতে পারেন রমাপদ। এই প্রত্যয়ে কোথাও কি লেগে আছে কিশোরবেলার সেই বিস্ময়ের আনন্দ! রমাপদ অ্যালবার্ট হলে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা শুনেছেন, দেখেছেন হিজলিতে রাজবন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে আসা মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধীকেও। কিন্তু বিস্ময়ের আনন্দ চিনেছেন অন্য মানুষকে দেখে।
কৈশোরে ভোরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনোটা অভ্যাস রমাপদর। ফেরেন খড়্গপুর স্টেশনের সুদীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে-হাঁটতে। সঙ্গে থাকে কুড়িয়ে আনা এক গুচ্ছ নাম না জানা সুগন্ধি ফুল। তার নাম দেওয়া হয়েছে, ‘বিলিতি চাঁপা’।
তেমনই এক দিন। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে। আচমকা, একটি খোলা জানলায় নজর আটকাল। স্পষ্ট নগ্ন নির্জন, স্বর্ণবর্ণ একটি হাত। পাঞ্জাবির হাতাটা কিছুটা গোটানো। রমাপদরা আসছেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ওই যাত্রীটি তাকিয়ে পশ্চিমের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে মনে হল, ভোরের সূর্যের আলোয় তন্ময় হয়ে আকাশ দেখছেন ‘কোনও ঋষিপুরুষ’। হাঁটা দিলেন রমাপদ। ফিরে এলেন, চিনতে পারলেন যাত্রীটিকে। মোহগ্রস্তের মতো উঠলেন কামরায়। পায়ের কাছে ‘বিলিতি চাঁপা’ রাখতে যাবেন, এমন সময়ে তা তুলে নিলেন যাত্রীটি। বললেন, “মুচকুন্দ? কোথায় পেলে?” ফুল চেনালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বেজে উঠল তখনই।
রমাপদ নামলেন ট্রেন থেকে, জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দটিকে সঙ্গে নিয়ে। হয়তো বা সে আনন্দই নিজের মতো করে জনসমুদ্রের পাড়ে বাঙ্ময় মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে রেখেছেন আপাত ভাবে নিভৃতচারী, অন্তর্মুখী সাহিত্যিকটি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।
তথ্যঋণ: উপন্যাস সমগ্র, গল্পসমগ্র, ‘হারানো খাতা’: রমাপদ চৌধুরী, ‘রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প’: শম্পা চৌধুরী, ‘রমাপদ চৌধুরী: বৈচিত্র ও অনুসন্ধান’ (সম্পাদনা, উত্তম পুরকাইত), ‘দেশ’, ‘কলেজস্ট্রীট’ এবং আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ