


পশ্চিমের আসন টলমল! বিশ্বনেতার তকমা হারাচ্ছে আটলান্টিকের পারের ‘সুপার পাওয়ার’রা। সেই তালিকায় রয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি। তাঁদের জায়গা নেওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে রাশিয়া এবং চিন। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিমকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে তুরস্ক ও ইরানও। এক কথায় ২১ শতকে দ্রুত গতিতে বদলাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতির ভরকেন্দ্র। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞেরা।
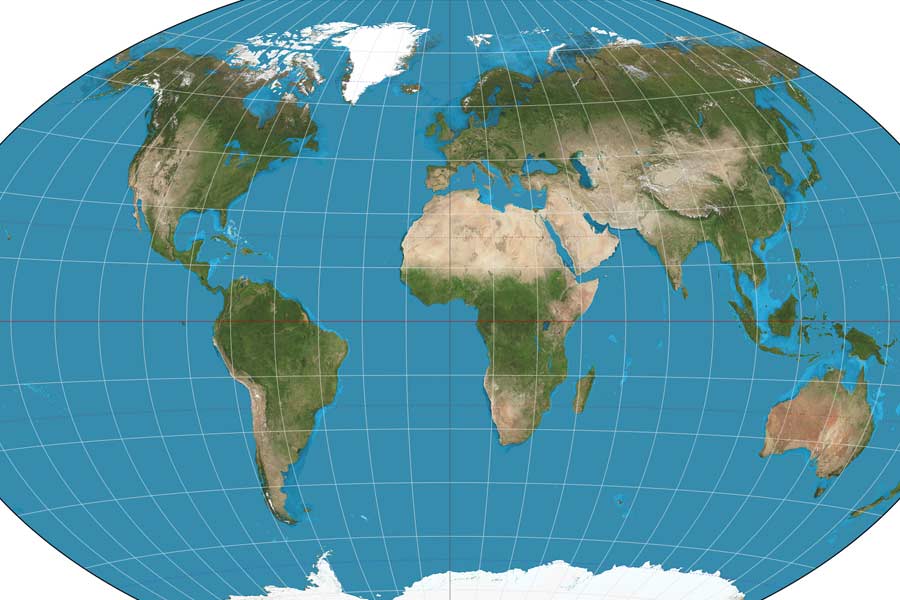
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক থেকে উপনিবেশ বিস্তারে কোমর বেঁধে লেগে পড়ে পশ্চিম ইউরোপের একাধিক দেশ। প্রথম দিকে পর্তুগাল এবং স্পেনের হাত ধরে এটা শুরু হয়েছিল। পরে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। এশিয়া, দুই আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তারা। বিশ্ব রাজনীতিতে উপনিবেশগুলির আলাদা করে যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। ফলে মূলত পশ্চিম ইউরোপের চার-পাঁচটি দেশের কথাতেই তখন চলত দুনিয়া।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পরিস্থিতির বদল ঘটে। ওই সময়ে ইউরোপের রাজনীতিতে প্রথম বার প্রবেশ ঘটে আমেরিকার। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ইউরোপ তথা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ‘লিগ অফ নেশন্স’ নামের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরির প্রস্তাব দেন। কিছু দিনের মধ্যে সেটি তৈরি হলে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশই এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। মজার বিষয় হল, লিগে যোগদান থেকে বিরত ছিল স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র।
প্রেসিডেন্ট উইলসন আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরির প্রস্তাব দিলেও মার্কিন পার্লামেন্ট কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ বা ‘সেনেট’ থেকে সেখানে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র পাননি তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদেরা তখনও তাঁর পূর্বসূরি জেমস মনরোর নীতি (মনরো ডকট্রিন) অনুসরণ করে চলছিলেন। সেখানে দু’টি বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেগুলি হল, আমেরিকা প্রথম নীতি (আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি) এবং ইউরোপের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা।
যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে লিগ প্রথম থেকেই ছিল দুর্বল। একে ঠিক ভাবে চালানোর দায়িত্ব এসে পড়ে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ঘাড়ে। তারা আবার এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে মস্কোর বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করছিল। কারণ, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সেখানে জমি শক্তি করে ফেলে কমিউনিস্ট সরকার। ধীরে ধীরে পূর্ব ইউরোপে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বের তত্ত্ব। তাতে প্রমাদ গুনেছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো অধিকাংশ দেশ।
গত শতাব্দীর ৩০-এর দশকে স্বৈরশাসনের দৌলতে বিশ্ব রাজনীতিতে আবির্ভাব হয় তিন মহাশক্তির। তারা হল, জার্মানি, ইটালি এবং জাপান। খুব কম সময়ে এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এই তিন রাষ্ট্র। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট-শাসিত রাশিয়ার লড়াই বাধাতে চেয়েছিল। ফলে লিগকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক দেশ দেখল করলেও বার্লিন, রোম বা টোকিয়োর ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে থাকছিল লন্ডন ও প্যারিস।
১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমেরিকা তখনও ইউরোপের রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যদিও লড়াই শুরুর দিন থেকেই বিপুল হাতিয়ার বিক্রি করে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে মার্কিন অর্থনীতি। ১৯৪১ সালে জাপান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে যুক্তরাষ্ট্রের নৌসেনা ঘাঁটিতে হামলা করলে যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে ওয়াশিংটন। এই সময়ে পুঁজিবাদী নীতির অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে কমিউনিস্ট রাশিয়ার হাত ধরতেও দ্বিতীয় বার ভাবেনি আমেরিকা।
১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ফের বদলায় বিশ্ব রাজনীতি। পরবর্তী তিন-চার বছরের মধ্যেই স্বাধীনতা পেয়ে যায় ব্রিটেন, ফ্রান্স বা স্পেনের যাবতীয় উপনিবেশ। জার্মানিকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করা হয়। নিজেদের সাম্রাজ্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে জাপান। অন্য দিকে, দুনিয়ায় শান্তি বজায় রাখতে আমেরিকার নেতৃত্বে জন্ম হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাল্লা ধীরে ধীরে ওয়াশিংটনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে কমিউনিস্ট রাশিয়ার (সোভিয়েত রাশিয়া) সঙ্গে আমেরিকার ‘বন্ধুত্ব’ দু’দিনও টেকেনি। দু’টি দেশ আলাদা আলাদা ভাবে ইউরোপ তথা বিশ্ব জুড়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ফলে দুই মহাশক্তির মধ্যে বেঁধে যায় ‘স্নায়ুর লড়াই’। এই সময়ে বিশ্বের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। যাঁর এক দিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অপর দিকে সোভিয়েত রাশিয়া।
১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতন হলে দুনিয়ার ‘রাজা’ হয়ে বসে আমেরিকা। বিশ্ব জুড়ে প্রভাব বিস্তারের জন্য পরবর্তী দশকগুলিতে উদারনীতির ব্যাপক প্রচার করেছিল ওয়াশিংটন। পাশাপাশি, অর্থনীতিকে মজবুত করতে পশ্চিম এশিয়ার উপর কড়়া নজর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। ধীরে ধীরে সেখানকার তেলের খনিগুলি কব্জা করতে থাকে মার্কিন সরকার। এর জন্য সেখানে পশ্চিমি সভ্যতার ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল আটলান্টিকের পারের ওই ‘সুপার পাওয়ার’।
যুক্তরাষ্ট্রের এ হেন পদক্ষেপকেই পশ্চিমের পতনের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞেরা। ১৯৭৯ সালে ‘ইসলামীয় বিপ্লব’-র পর কট্টর শিয়াপন্থীদের হাতে চলে যায় ইরানের শাসনভার। পশ্চিমি সংস্কৃতিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেন সেখানকার ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেইনি। ধীরে ধীরে আরব মুলুকগুলিতে ইসলামীয় মৌলবাদ পা জমাতে শুরু করে। এঁদের চোখে মূল শত্রু হল আমেরিকা ও পশ্চিমি বিশ্ব।
অন্য দিকে গোটা ‘স্নায়ু যুদ্ধ’ পর্বে মুখ বন্ধ রেখেছিল চিন। এই সময়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নতির দিকে নজর দেয় বেজিং। ৯০-এর দশকের পরবর্তী সময়ে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের জন্যও দরজা খুলে দেয় ড্রাগনভূমি। সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা থাকায় এই দেশগুলি সেখায় একের পর এক কারখানা খুলতে শুরু করে। ফলে রকেট গতিতে দৌড়তে শুরু করে চিনের অর্থনীতি।
‘ঠান্ডা লড়াই’ পর্বে সোভিয়েত আগ্রাসন ঠেকাতে ১৯৪৯ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে তৈরি হয় ‘উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন’ (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজ়েশন) বা নেটো শক্তিজোট। তাতে যোগ দেয় পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ। নেটোর পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনও দেশ এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোনও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলে সমস্ত সদস্য দেশগুলি সামরিক দিক থেকে তাকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।
গত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে সোভিয়েতের পতনের পরও ইউরোপে নেটোর বিস্তার ঘটায় আমেরিকা। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২। ইউরোপীয় দেশগুলি নেটোয় যোগ দিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা বাজেট কমিয়ে যৎসামান্য করে দেয়। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খরচ। এতে মার্কিন অর্থনীতিতে চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
১৯৭৯-র ‘ইসলামীয় বিপ্লব’-এর পর রাজধানী তেহরানের মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালায় ইরানের উগ্রপন্থী ছাত্রেরা। ৬৩ জন আমেরিকানকে পণবন্দি করেন তাঁরা। উদ্ধারে সেনা অভিযানের নির্দেশ দেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। এর নাম ছিল ‘অপারেশন ঈগল ক্ল’। কিন্তু, এই অভিযানে ব্যর্থ হন যুক্তরাষ্ট্রের কমান্ডোরা। এর জেরে ৪৪৪ দিন ধরে তেহরানে পণবন্দি ছিলেন দূতাবাসের মার্কিন নাগরিকেরা।
‘অপারেশন ঈগল ক্ল’-এর ব্যর্থতার জেরে আমেরিকার বিশ্বনেতা হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে পড়ে। এর পর ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-সহ একাধিক জায়গায় আত্মঘাতী হামলা চালায় কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন ‘আল-কায়দা’। এতে দ্বিতীয় বার বড় আকারের ধাক্কা খায় মার্কিন আধিপত্য। ফলে কতকটা বাধ্য হয়েই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয় যুক্তরাষ্ট্রকে।
২১ শতকের গোড়ার দিকে ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী হাতিয়ার থাকার অভিযোগ তোলে আমেরিকা। একে কেন্দ্র করে ২০০৩ সালে বাগদাদ আক্রমণ করে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তা-ই নয়, এই সময়ে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধেও জড়িয়েছিল মার্কিন সরকার। কিন্তু এত কিছু করেও আরব মুলুকগুলিতে পশ্চিমি সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ছড়িয়ে দিতে পারেনি ওয়াশিংটন। উল্টে সেখানে জন্ম হয় নতুন জঙ্গি সংগঠনের। নাম ‘ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া’ বা আইসিস।
অন্য দিকে নেটোর বিস্তারকে কেন্দ্র করে ইউরোপে নতুন করে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। রুশ সীমান্ত পর্যন্ত একে ছড়িয়ে দিতে ইউক্রেনকে দলে টানার চেষ্টা করেন এই শক্তি জোটের মাথারা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে প্রমাদ গোনে মস্কো। এ ব্যাপারে কিভকে বার বার দূরে থাকার হুঁশিয়ারি দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাতে কাজ না হওয়ায় ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে ‘বিশেষ সেনা অভিযান’ (স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন) চালাচ্ছেন তিনি।
গত তিন বছর ধরে চলা রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বিশ্ব রাজনীতি সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। লড়াইয়ের প্রথম দিকে আমেরিকা কিভকে সমর্থন করলেও এখন আর তা করতে নারাজ বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তা-ই নয়, ইতিমধ্যেই নেটো ত্যাগের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। এতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
বিশ্লেষকদের অবশ্য দাবি, এটা না করে আমেরিকার কাছে দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। কারণ নেটোর নামে গোটা ইউরোপের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে বিপুল ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার মরিয়া চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। আর তাই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
পশ্চিম ইউরোপের দ্বিতীয় বড় সমস্যা হল শরণার্থী। এর জন্য বিশ্লেষকেরা অবশ্য আমেরিকাকেই দায়ী করে থাকেন। ইরাক ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপের জেরে বাস্তুচ্যুত হন সেখানকার হাজার হাজার মানুষ। তাঁদেরই একটা বড় অংশ ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ঢুকে পড়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে। ফলে জার্মানি ও ইটালির মতো দেশগুলিতে ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ওয়াশিংটনের উদারনীতিবাদ। সেখানকার রাজনীতিতে পা জমাতে শুরু করেছে চরম দক্ষিণপন্থীরা।
বিশ্লেষকদের অনুমান, ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সোভিয়েতে আমলের পুরনো গৌরব ফিরে পেতে চাইছে রাশিয়া। একই কথা তুরস্কের ক্ষেত্রেও সত্যি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব অটোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ‘ইউরোপের রুগ্ন মানুষ’টিকে কেন্দ্র করেই। বর্তমানে সেই আসন ফিরে পেতে আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় লাগাতার ক্ষমতা প্রদর্শন করে চলেছেন সেখানকার প্রেসিডেন্ট রিচেপ তায়িপ এর্ডোগান।
এ হেন পরিস্থিতিতে ফের এক বার ‘আমেরিকা প্রথম’ নীতিতে ফিরে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তাতে অবশ্য ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় থামছে না চিনের ‘দাদাগিরি’। এর মাধ্যমে সরাসরি ওয়াশিংটনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে বেজিং। কারণ বিশ্ব নেতা হওয়ার অন্যতম দাবিদার হিসাবে নিজেকে দেখছে ড্রাগন। আর্থিক দিক থেকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকাকে তারা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
২১ শতকে বিশ্বের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র আর এক দিকে ঝুঁকে নেই। নানা ক্ষেত্রে এটি ছড়িয়ে পড়েছে। পুরনো জোটগুলি ভেঙে গিয়ে ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে নতুন সংগঠন। তার মধ্যে ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের ‘কোয়াড’ বা ভারত, ইজ়রায়েল, আমেরিকা ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে নিয়ে তৈরি ‘আইটুইউটু’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন দেশ দুনিয়ার ‘রাজা’ হওয়ার তকমা ছিনিয়ে নেবে, তার উত্তর দেবে সময়।