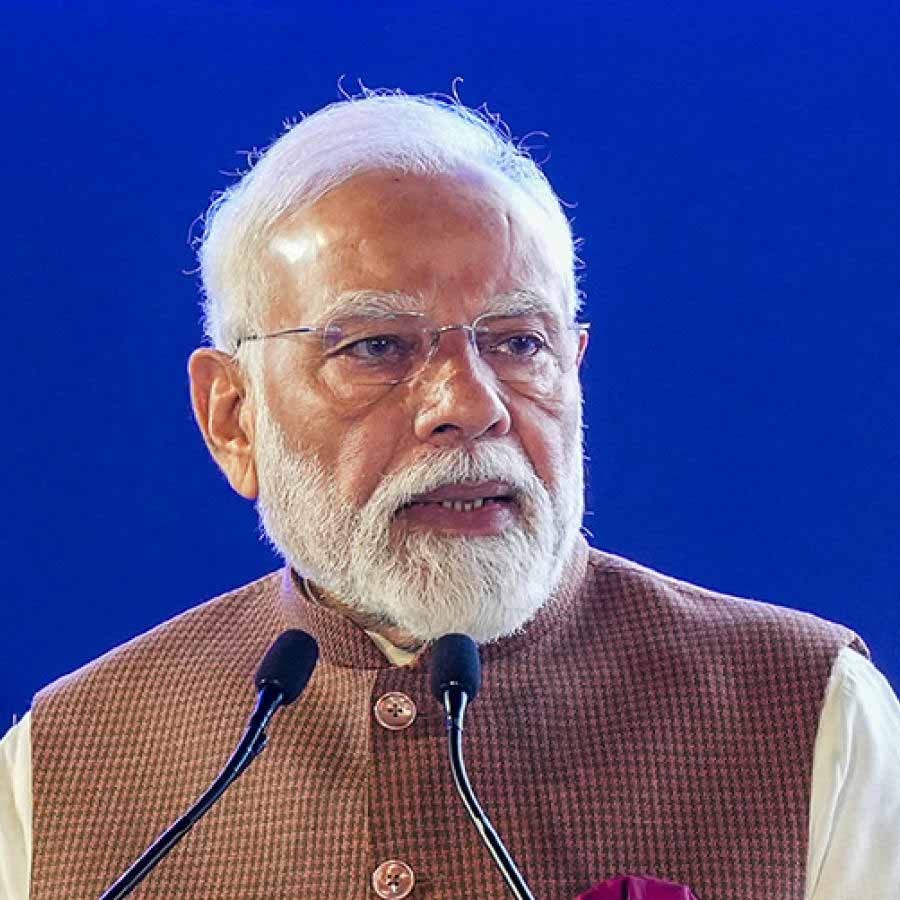বহুত্বের বিরোধী
শীর্ষ আদালতে বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া বললেন, উর্দু ভারতের গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতির উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত, এ ভাষার জন্ম ভারতেই— তাকে কোনও ধর্মের সঙ্গে এক করে দেখা চলতে পারে না।

ভাষা ধর্ম নয়। এমনকি, ভাষা কোনও ধর্মের প্রতিনিধিত্বও করে না। ভাষার সম্পর্ক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।” ভারতের সৌভাগ্য যে, গোটা দেশের উপরে একশৈলিক হিন্দুত্ব ও তার অনুষঙ্গ চাপিয়ে দেওয়ার গৈরিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য এখনও শীর্ষ আদালতের উপরে ভরসা করা যায়। মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার এক পুরসভার সাইনবোর্ডে উর্দুতে লেখা নিয়ে আপত্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল শীর্ষ আদালতে। তার আগেই বম্বে হাই কোর্ট জানিয়েছিল যে, উর্দু সংবিধান-স্বীকৃত ভাষা, ফলে পুরসভার সাইনবোর্ডে সে ভাষার ব্যবহারে আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। এ বার শীর্ষ আদালতে বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া বললেন, উর্দু ভারতের গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতির উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত, এ ভাষার জন্ম ভারতেই— তাকে কোনও ধর্মের সঙ্গে এক করে দেখা চলতে পারে না। বস্তুত, ভাষা অথবা ভারত, কোনও ইতিহাস সম্বন্ধেই ধারণা থাকলে হিন্দুত্ববাদীরা বুঝতেন, যে উর্দুর তাঁরা ঘোর বিরোধী, আর যে হিন্দির তাঁরা প্রবল সমর্থক, মহারাষ্ট্রেরই বিদ্যালয়ে যে হিন্দিকে তাঁরা আবশ্যিক তৃতীয় ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর— দুই ভাষার উৎস এক, উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষার সংমিশ্রণে। আমির খসরু যাকে ‘হিন্দভি’ ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তার থেকে জন্ম নিয়ে, ঔপনিবেশিক শাসন-রাজনীতি-অর্থনীতি-প্রযুক্তি-ক্ষমতার বিবিধ চড়াই-উতরাই পার হয়ে আজ ভাষা দু’টি নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছে। উর্দুকে অস্বীকার করতে চাওয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতের ইতিহাসকেই অস্বীকার করতে চাওয়া। হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীরা অবশ্য ভারতের ইতিহাস নিয়েও বিশেষ ভাবিত নন— রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে সে ইতিহাস তাঁরা যথেষ্ট পাল্টে নিতে চান।
শুধু ভারতে নয়, দুনিয়ার সর্বত্রই একাধিপত্যকামী শাসন সাংস্কৃতিক বহুত্বকে অস্বীকার করতে চায়। নিজেদের সঙ্কীর্ণ ‘বিশ্ববীক্ষা’-র সঙ্গে যেটুকু খাপ খায়, শুধু সেটুকুকেই রেখে বাকি সব কিছুকে ফেলে দিতে চায়। এবং, প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে ব্যবহার করে একটিই যুক্তি— ‘এগুলি দেশের বা জাতির সংস্কৃতির অংশ নয়’। ভারতের হিন্দুত্ববাদ মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের উচ্চ ও মধ্যবর্ণ হিন্দু জাতিসত্তার সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত, ফলে তার বাইরে আর যা কিছু, তাদের যুক্তিতে সবই বর্জনীয়। উর্দুর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়া, আর নবরাত্রি উপলক্ষে বাজারে আমিষ বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া আসলে একই সাংস্কৃতিক উদ্বেগের ফল— হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্কীর্ণ মস্তিষ্ক এই বহুত্বকে হজম করতে পারে না। ভারত নামক ধারণাটির সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের দ্বন্দ্বের প্রধানতম কারণ এখানেই নিহিত। নিজে যা নই, তাকেও স্বীকার করতে পারার উদারবাদের জন্য যে শিক্ষা এবং মানসিক প্রসার প্রয়োজন, নাগপুরের পাঠশালায় দুর্ভাগ্যক্রমে তার চর্চা হয় না। রাজনৈতিক হিন্দুত্বের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসের প্রতিটি মুহূর্তই এই অসহিষ্ণুতার সাক্ষ্য বহন করে— অধুনা রাজনৈতিক ক্ষমতা তাকে প্রবল করেছে।
বিচারপতি ধুলিয়ার রায় শিরোধার্য। তার পরেও কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, সত্যিই যদি উর্দু ভাষার সঙ্গে মুসলমান ধর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হত, তাতেই বা কী? সংবিধান এখনও ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসাবেই চিহ্নিত করে। তাকে সঙ্কীর্ণতম অর্থে ব্যাখ্যা করতে হলেও বলতে হয়, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত করতে পারে না, কোনও বিশেষ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণও করতে পারে না। রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে সংযোগহীন থাকতে হয়। কোনও সাংস্কৃতিক অভ্যাস মূলত মুসলমানদের, সেই কারণেই রাষ্ট্র তার বিরোধিতা করবে— ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এই অবস্থান সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার্য। হিন্দুত্ববাদীদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভোটে জিতে তাঁরা শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন বটে, কিন্তু দেশের মালিক হয়ে যাননি। দেশের চরিত্র পাল্টে দেওয়ার কোনও অধিকার তাঁদের নেই।