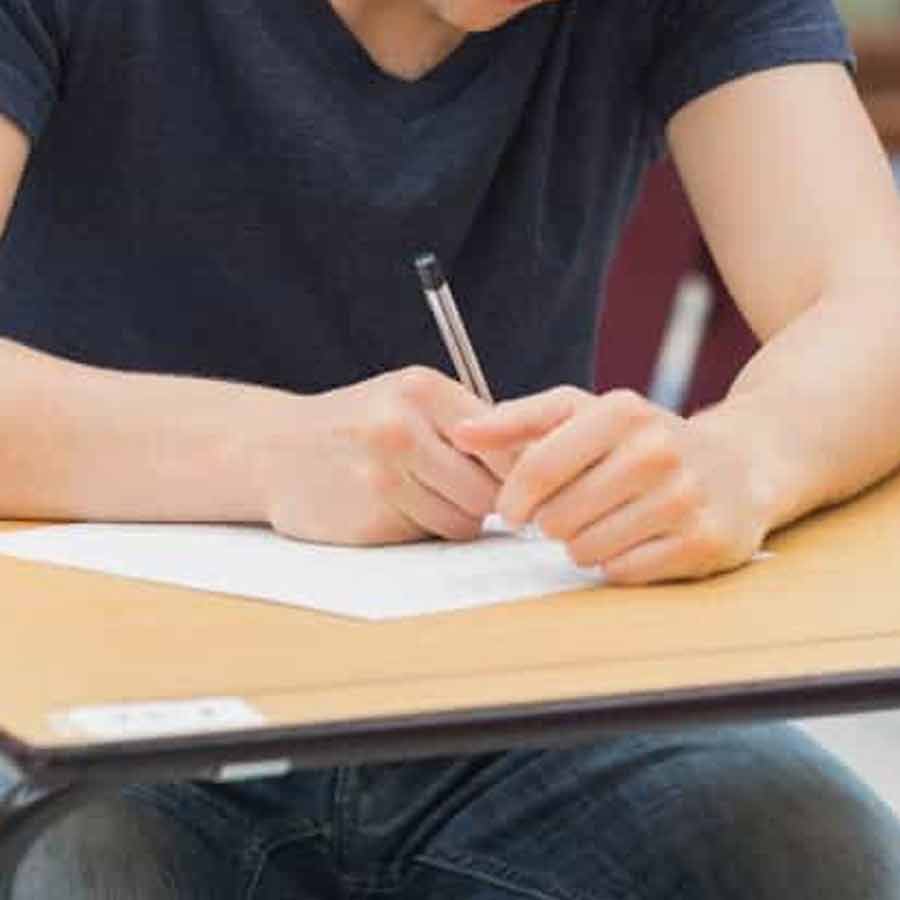সময়ের অনুভব
প্রশ্নটি বহুমাত্রিক, দ্যোতনাময়। ঘড়ি-ক্যালেন্ডার যতই সকলকে বাঁধতে চায় একই গতি-ছন্দে, যৌবন-চেতনার উন্মেষ সকলের মনে একই বয়সে আসে না।

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কয়েকটি অসামান্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন। শ্রুতলিপি আকারে তৈরি হয়েছিল ‘কত্তামশাই’ (প্রকাশ ১৩৭৯), এক দৃষ্টিহীন মানুষের নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আখ্যান। বিশেষ ভাবে স্পর্শ করে যায় সময় কত হল, তা বোঝার চেষ্টাটি। বেলা কত হল, তা বুঝতে দিনের নানা সময়ের নানা শব্দকে গুনেগেঁথে রাখেন মনে মনে। কুক পাখির ডাক, দুধওয়ালার সাইকেল, ফেরিওয়ালার ডাক, এগুলি তাঁর জগতের এক-একটি ঘণ্টা। তাতেও সব দিন কুলোয় না। এক দিন পরিচারক চা দিলে প্রশ্ন করেন, ন’টা তো বাজেনি, এখনই চা কেন? সে উত্তর দেয়, দশটা বেজে গিয়েছে। কিন্তু ট্রেনের আওয়াজ তো শোনা যায়নি? “আজ্ঞে আজ হরতাল। ট্রেন বন্ধ,” উত্তর এল। “কত্তামশায়ের সামনে থেকে সেদিনের ন’টা বাজা সকালটা হারিয়ে গেল।” তেমনই, একটা বিকেল হারিয়ে যায়, যখন পাঁচটা বাজার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে শেষে শোনেন পাশের বাড়ি থেকে বাসন মাজার শব্দ আসেনি, কারণ সহায়িকা মেয়েটি পালিয়ে গিয়েছে। মানুষের উপর নির্ভর করা ছেড়ে তাই কত্তামশাই ঝুঁকলেন প্রকৃতির দিকে— “মৌচাকের খোপে খোপে যেমন মধু রয়েছে তেমনি সময়ের খোপে খোপে প্রকৃতির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।” কত্তামশাইয়ের বেদনায় সিক্ত হতে হতে মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষের দেহও কি প্রকৃতির মৌচাকের একটি খোপ নয়? সমুদ্রতলে, ভূগর্ভে কত না জীব বাস করে। তাদের জন্ম-প্রজনন-মৃত্যুর ছন্দে কোনও ছেদ পড়ে না। যেখানে আলো নেই, বাইরে থেকে কোনও ইঙ্গিত নেই সময়ের পরিবর্তনের, সেখানে জীবের অন্তরই কেন তাকে বলে দেবে না, কত সময় কেটে গিয়েছে, আর কতটা সময় বাকি রয়েছে?
প্রশ্নটি বহুমাত্রিক, দ্যোতনাময়। ঘড়ি-ক্যালেন্ডার যতই সকলকে বাঁধতে চায় একই গতি-ছন্দে, যৌবন-চেতনার উন্মেষ সকলের মনে একই বয়সে আসে না। দুঃখের রাত যেন কাটতে চায় না, আর আনন্দের দিন যেন মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়। ছেলেবেলার ঘটনাকে মনে হয়, সে দিনের কথা। আর বছর দু’তিন আগের কোনও মামুলি বৈষয়িক কথা সহজেই চলে যায় বিস্মৃতিতে— অত দিন আগের কথা কি মনে থাকে? সুররিয়ালিস্ট শিল্পী সালভাদর দালির আঁকা ‘দ্য পার্সিসটেন্স অব মেমরি’ ছবিতে দেখা যায় গলে-যাওয়া নানা ঘড়ি, গাছের ডালে ঝোলানো কিংবা মেঝেতে লেপ্টানো। এগুলি আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত, কিন্তু এর নিহিত অর্থ সহজেই দর্শককে স্পর্শ করতে পারে। সময় যে একরৈখিক, একমুখী নয়, তা নমনীয়, সময়ের অনুভব সতত পরিবর্তনশীল, এক (দুঃ)স্বপ্নময় প্রেক্ষিতে ঝুলন্ত, গলন্ত ঘড়িগুলোকে দেখে সেই অনুভবই হয়।
বিজ্ঞানীরা অবশ্য এমন অস্পষ্ট উত্তরে খুশি নন। তাঁদের প্রশ্ন সোজা-সাপটা— দিন আর রাত, গরম আর শীতলতার অনুভব থেকে বিচ্ছিন্ন ‘বায়োলজিক্যাল ক্লক’ বলে কি মানুষের সত্যিই কিছু হয়? বরাবরই ক্ষীণদৃষ্টি বিনোদবিহারী ১৯৫৬ সালে ছানি অপসারণের অস্ত্রোপচারের পর সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তার ছ’বছর পরে এক ফরাসি ভূতাত্ত্বিক মিশেল সিফ্রা নিজের উপর এক ভয়ানক পরীক্ষা করেছিলেন। আল্পস পর্বতে, মাটির ১৩০ মিটার নীচে, মোট তেষট্টি দিন কাটিয়েছিলেন তিনি। বাইরের আলো ঢোকে না, সময় বোঝার কোনও উপায় ছিল না। দেখা গেল, তাঁর জৈব ঘড়ি অনেক ধীরগতি হয়ে গিয়েছে, তাঁর জেগে থাকার সময় ক্রমশ দীর্ঘ হয়েছে, একশো কুড়ি গুনতে তাঁর লেগে গিয়েছে পাঁচ মিনিট। তাঁকে অনুসরণ করে যাঁরা এই ধরনের পরীক্ষা করেছেন নিজেদের উপর, তাঁদের এক জন এক সঙ্গে তেত্রিশ ঘণ্টাও ঘুমিয়েছেন। কেউ বা তিন দিন টানা জেগে থেকেছেন। এই ধরনের পরীক্ষা অবশ্য এই বেপরোয়া বিজ্ঞান-সাধকদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি করেছে। তবে এই বিজ্ঞানীদের কাজ থেকে তৈরি হয়েছে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা, হিউম্যান ক্রোনোবায়োলজি। দীর্ঘ দিনের মহাকাশযাত্রার জন্য নভশ্চরদের প্রস্তুত করার উপায় খোঁজায় বিজ্ঞানের এই শাখাটি বিশেষ কাজে আসে। লেখক সামান্থা হার্ভে তাঁর বুকার-জয়ী অরবিটাল উপন্যাসে দেখিয়েছেন, চব্বিশ ঘণ্টায় ষোলো বার সূর্যোদয় দেখার অভিঘাত কেমন হতে পারে মহাকাশযানে পৃথিবী আবর্তনরত মানুষগুলির মনে। অন্ধকারে আবদ্ধ বিজ্ঞানীরা যে জ্ঞানের আলো দিয়ে গিয়েছেন, তাতে অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে কত্তামশাইয়ের কাজটি কত কঠিন ছিল। সময়ের ছন্দ ছাড়া আমাদের জীবন ছন্নছাড়া। দিন আর রাত, বসন্ত আর বর্ষা সময়ের গতির নির্দেশ দিয়ে যায়, ইন্দ্রিয়ের ভিতর ঘা দিয়ে যায়, আমাদের চিত্তও সেই মৃদঙ্গের বোলে কথা বলে।