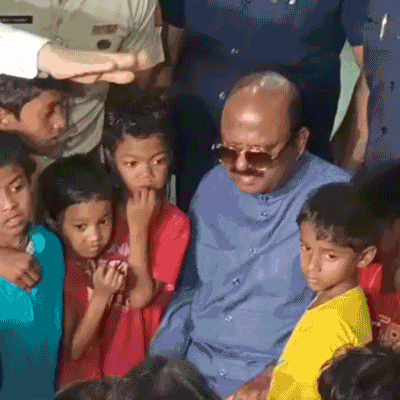ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি শুধু পূর্ববঙ্গের নয়, রাঢ়বঙ্গেরও বটে
যে বাংলাদেশের মেয়েদের চোখে এত মেঘের আনাগোনা, সেই বাংলাদেশের মায়েরাই বলতে পারেন, “সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি। একা।”
বিশ্বজিৎ রায়

চলে যাওয়া নয়, থেকে যাওয়াটাই যে এক রকম প্রতিবাদ, তা বুঝতে পেরেছিলেন হাসান আজিজুল হক। কারণ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন এক নারী। নিচ্ছেন তাঁর ছেলে আর স্বামীর মতের বিরুদ্ধে গিয়েই। এক দিন শ্বশুরবাড়িতে এসে তাঁর অক্ষরপরিচয় হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়-এর পাতায় পাতায় মিশেছিল তাঁর চোখের পানি। সারা দিন সংসারের কাজ সামলে রাতে বর্ণপরিচয়-এর অক্ষর চেনার কাজ খুব সহজ ছিল না। সেই কঠিন কাজটি করতে পেরেছিলেন বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবর নিয়ে যখন বর্ধমানের গ্রামে এসে পৌঁছত বঙ্গবাসী, তখন পড়তে পারতেন। সবটা যে বুঝতে পারতেন, তা নয়; যাঁর উপর নির্ভর করতেন, সেই মানুষটিও তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন অনেক কথা।
নির্ভর করবেন না-ই বা কেন! তাঁর কত্তা মানুষটি তো যেমন তেমন নন, হিন্দু-মুসলমান দু’পক্ষেরই চোখের মণি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়ে রেল স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা তৈরির সময় জায়গায় জায়গায় রাস্তাটিকে একটু বাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে রাস্তা সোজা হল না বটে, তবে কত গরিব চাষির অল্পস্বল্প জমি রাস্তার কবল থেকে বেঁচে গেল। সোজা নিরেট রাস্তার উন্নয়নের নামে যে জমি আর গরিবের মাথা কাটা পড়ার কথা তা পড়ল না। সে বার যখন গাঁয়ে আগুন লাগল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল আধখানা গ্রাম, তখন কত্তাই গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সম্পন্ন চাষিদের কাছে হাত পেতে আবার গড়ে তুলেছিলেন পুড়ে যাওয়া মানুষের ঘরবাড়ি। ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণকে গিয়ে বলেছিলেন তাঁর সদ্য-জন্মানো ছেলের নাম বদলে দিতে। ভন্ডুল হয়নি কিছুই, ঘরবাড়ি তো আবার গড়ে নেওয়া গিয়েছে, তা হলে ছেলের নাম সেই আগুনের ছত্রভঙ্গতার আদি মুহূর্ত মেনে কেন রাখা হবে ভন্ডুল!
সব অবশ্য আটকানো যায় না শেষ অবধি। হিন্দু-মুসলমানের ‘হিড়িক’ আটকানো যায়নি। মুসলমানরা হিন্দুদের মারে, হিন্দুরা মারে মুসলমানদের। রায়দের বাড়ির ছেলে কলকাতায় কাটা পড়ল। শোকগ্রস্ত মায়ের কাছে গিয়েছিল সে; সে যে মুসলমান বাড়ির বৌ, যাওয়ার সময় সে কথাটা ততটা মনে হয়নি। সেখানে গিয়ে মনে হল। “রায় গিন্নি কাকে ঘিন্ করবে বুঝতে পারছে না, বোধায় আমাকেই তার ঘিন্ লাগছে। কি দোষ দোব রায়গিন্নির? ঐ মা তার ছেলের লাশটো-ও দেখতে পায় নাই।” মুসলমান মায়ের বুকও কি খালি হল না? হল তো একই ভাবে। “শুনতে প্যালম পাশের গাঁয়ের মোসলমানদের একটি ছেলে জেলার বড় শহরে স্কুলে পড়ত... খাঁড়া বগী ছোরা ছুরি কিরিচ নিয়ে একদল হিঁদু যেয়ে তাকে কেটে কুচি কুচি করলে।” এর ফল দেশভাগ— আটকানো গেল না। তবে এই গাঁ-ঘরের বৌটি আটকাতে না পারলেও তাঁর মতো করে প্রতিবাদ করলেন শেষ অবধি। ছেলে আর কত্তার কথা মেনে নিলেন না। কত্তাকে তিনি নির্ভর করতেন, নির্ভর করেন— তবু উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর: “আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।”
আগুনপাখি উপন্যাসটি যখন ২০০৫ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন হাসান আজিজুল হক এর নাম দিয়েছিলেন ‘অপরূপকথা’। সে নামের মধ্যে রূপকথা শব্দটি লুকিয়ে ছিল। রূপকথায় যা ঘটে, বাস্তবে তা সব সময় হয় না, এ-ও যেমন সত্য— তেমনই বাস্তবে যা হয়, হতে পারে, রূপকথায় তা অন্য ভাবে বড় করে দেখানো চলে, সে-ও সমান সত্য। বর্ধমানের কোনও এক গ্রামের মুসলমান বাড়ির বৌ পুরুষদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে ভারতে থেকে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিলেন, তা ‘অপরূপকথা’।
এ উপন্যাস লেখার সময় হাসান সাহিত্য-সত্যের উপর ভর করেছিলেন। সে বিশেষ দেশের কালের সাহিত্যমাত্র নয়, দেশ-বিদেশের নির্বিশেষ সাহিত্য-সত্য। সবুজপত্র-এ এক দিন বাঙালি পড়েছিল মৃণালের কথা। রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের মৃণাল বাড়ি থেকে, তার স্বামীর কলকাতার বাড়ি থেকে শ্রীক্ষেত্রে চলে গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিল চিঠি লিখে। মৃণালের সে চিঠির ভাষায় গাঁ-ঘরের বুলি নয়, রবীন্দ্রনাথের মান্য-চলিত আত্মপ্রকাশ করেছিল। হাসানের চরিত্রটি গ্রাম্য বুলিতেই নিজের কথা বলে। আর, সেটাই বাস্তবের ভাষার নিকটবর্তী। এ উপন্যাসের শেষে চলে গিয়ে নয়, ভারতে থেকে গিয়ে মেয়েটি তার নিজের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করল। শেষে যখন সে বলে, “আমি একা। তা হোক, সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি। একা।”— তখন ইবসেনের অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল নাটকের ডাক্তার স্টকম্যানের সংলাপ মনে পড়ে যায়: “...দ্য স্ট্রংগেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ় হি হু স্ট্যান্ডস মোস্ট অ্যালোন।” সত্যজিৎ যখন গণশত্রু ছবি নির্মাণ করেছিলেন, তখন এই একাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বহু-র ব্যঞ্জনায়। সত্যজিতের ছবির শেষে দেখা যায় ধর্মান্ধ মন্দির-ব্যবসায়ীদের মতের বিরুদ্ধে জেগে উঠছে সাধারণ মানুষ। তাঁরা যে ডাক্তারের সঙ্গে আছেন সে ইঙ্গিত ছিল ছবির শেষে। আগুনপাখি-র গাঁ-ঘরের বৌটি বললেন, একা হলেও সবাইকে বুকে টানতে পারবেন তিনি।
ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিকতার মুহূর্তগুলি কেবল স্বাতন্ত্র্যের একাকিত্বে আত্মপ্রকাশ করে না, তার মধ্যে সামাজিক বহু-র স্মৃতি জেগে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হল। দেশভাগ হল বটে, তবে তার আগের স্মৃতি মিথ্যা হয়ে গেল না। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ছিল, কিন্তু তা দেশভাগের দিকে ঠেলে দিত না। গাঁ-ঘরের হিন্দু-মুসলমান মানুষের মধ্যে রাজনীতির অঙ্ক কষে ‘ঘিন্’ জাগিয়ে তোলার ঔপনিবেশিক দস্তুর, তা প্রাগাধুনিক বঙ্গদেশের পল্লির সত্য ছিল না। প্রাগাধুনিক বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য-সংঘাত আর রাজনৈতিক অঙ্ক কষে রাষ্ট্রপোষিত দাঙ্গা এক নয়।
দেশভাগের সময় ভারতে থেকে গিয়েছিলেন যে মুসলমানেরা, যাঁদের ন্যাশনালিস্ট মুসলমান বলার দস্তুর তৈরি হয়েছিল, তাঁদের পাশে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট হিন্দুরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই বড় ইতিহাসের খবর অনেকটাই জানা। ২০০৫-এ ‘অপরূপকথা’য় মুসলমান বাড়ির এই বৌটির মুখ দিয়ে যে সত্যে হাসান উপনীত হয়েছিলেন তা এই উপমহাদেশের, পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি হিন্দুদের মনে রাখা জরুরি ছিল। ফেলে আসা গ্রাম বলতেই সচরাচর বাঙালি হিন্দুরা পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে কাতর হতেন। স্মৃতি যে একপাক্ষিক নয়, বহুপাক্ষিক হতে পারে, ফেলে আসা গ্রাম যে রাঢ়বঙ্গেও থেকে যায়, এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল এই উপন্যাস।
বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষাও যে এক রকম নয়, তা-ও মনে করিয়ে দিয়েছিল আমি-পক্ষের বয়ানে লেখা এই আখ্যান। হাসানের মা যে বাংলা-বুলি ব্যবহার করতেন, তাঁর ফুফুরা বা চাচিরা সে ভাবে কথা বলতেন না। দেশভাগ নিয়ে পুরুষ ও নারীর বয়ান এক রকম হয় না। মেয়েদের বয়ানে দৈনন্দিনের এমন অনেক টুকিটাকি থাকে, যা হয়তো পুরুষের চোখেই পড়ে না। সুনন্দা সিকদারের দয়াময়ীর কথা-তে ফেলে আসা পূর্ববঙ্গের দিঘপাইত গ্রামের কত অন্তরঙ্গ ছবি, সে ছবির গায়ে লেগে আছে গাঁ-ঘরের বুলি আর ছড়া। সে ভাষা ছাড়া ছবি অসম্পূর্ণ। শ্রীমতী শোভা ঘোষের বই যেন ভুলে না যাই (১৩১০) প্রকাশ করেছিল বরিশাল সেবাসমিতি। পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা পল্লির নানা জায়গার নানা ভাষা। সেই নানা ভাষার নমুনা যাতে ভুলে না যান, সে জন্যই সে পুস্তিকাতে ধরে রাখা হয়েছিল নানা ভাষাভেদের উদাহরণ। হিন্দু বাঙালি অনেক রকম, মুসলমান বাঙালিরও নানা ভেদ, তাঁদের বাংলা বুলির মধ্যেও নানা ছাঁচ। এই সমস্ত ভেদ নিয়েই তাঁদের থাকা। সেই থাকাটা বিপন্ন হয় তখনই, যখন ভেদগুলি মুছে আত্মপরিচয়ের কৃত্রিম একটা রংচঙে নকল কাঠামো তৈরির হিড়িক ওঠে।
বিচিত্রা পত্রিকায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্ থেকে প্রকাশিত জসীমউদ্দিনের নক্সী কাঁথার মাঠ কাব্যের সমালোচনা করেন দীনেশচন্দ্র সেন। লেখেন, পল্লির মেয়েরা মেঘগুলিকে যে কত নামে ডাকে, জসীমউদ্দিনের কাব্য পড়লে বোঝা যায়। “‘কালো মেঘা’ নামো নামো, ‘ফুল তোলা মেঘ’ নামো/ ‘ধূলট মেঘা’ ‘তূলট মেঘা’, তোমরা সবে ঘামো।/ ‘কানা মেঘা’ টল্ মল্ বার মেঘার ভাই,/ আরো ‘ফুটিক’ ঢলক দিলে চীনার ভাত খাই।” যে বাংলাদেশের মেয়েদের চোখে এত মেঘের আনাগোনা, সেই বাংলাদেশের মায়েরাই বলতে পারেন, “সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি। একা।”
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী